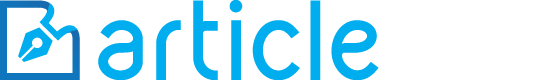যুবায়ের আহমাদঃ একটি জাতির পরিবর্তনের জন্য দরকার একজন নেতা। মুসা আ. বনি ইসরাঈলে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, ইবরাহিম আ. নমরূদের মসনদে আঘাত হেনে আল্লাহর বড়ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনি একজন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব মানবতার ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় মুহাম্মদ বিন কাসিম তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে এই উপমহাদেশের মানুষকে আত্মিক মুক্তির সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন তিতুমীরের ডাকে বাংলার নিপীড়িত মজলুম জনতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো।
মানুষ শিক্ষিত হয় মানুষের জন্য। জ্ঞানার্জনের পরই একজন মানুষ স্বজাতির কাছে ঋণী হয়। পথহারা মানুষের পাশে দাঁড়াতে। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ পরলৌকিক মুক্তির পথকে সুগম করার সামাজিক দায়বদ্ধতা চেপে বসে শিক্ষিত মানুষের ঘাড়ে। ভারতীয় উপমহাদেশে যে ক’জন মনিষী এ ঋণ নিঃস্বার্থভাবে শোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদেরই একজন মাওলানা আতহার আলী রহ.।
ইতিহাসের এ কিংবদন্তি ১৮৯১ সালে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই গ্রামের মক্তবে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। প্রাথমিক শিক্ষা ঝিঙ্গাবাড়ি আলিয়া মাদরাসা ও বেশ ক’জন বুজুর্গ আলেমের কাছে সম্পন্ন করে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভারতে যান। মাদরাসায়ে কাসেমিয়া শাহি মুরাদাবাদ, মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর এবং সর্বশেষ মাদরাসায়ে আলিয়া রামপুরে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং অত্যন্ত কৃতিত্যের সঙ্গে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও শাইখুল ইসলাম আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানী রহ. অন্যতম।
শিক্ষা সমাপনান্তে মাওলানা আতহার আলী রহ. আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবীর রহ. পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। মুরশিদের সান্নিধ্যে থেকে কঠোর পরিশ্রম ও মুজাহাদার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির স্তরসমূহ অতিক্রম করে খুব অল্প সময়ে তার খেলাফত লাভে ধন্য হন।
বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী এ মহান আলেম স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর নিজ গ্রামে ইলমে হাদিস শিক্ষাদান শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে যোগ্যতার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তিনি সিলেট জেলার প্রাচীন ও বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঝিঙ্গাবাড়ি আলিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দেশের বিভিন্ন মাদরাসা থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসতে থাকে। অবশেষে কুমিল্লা জামিয়া মিল্লিয়াতে মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি যেমন ছিলেন দক্ষ ও সুযোগ্য তেমনি তার ব্যক্তিত্ব ছিলো বিশাল ও গুরুগম্ভীর। এ কারণেই ছাত্রসমাজে তিনি যেমন ছিলেন প্রিয়পাত্র, মাদরাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছেও ছিলেন সম্মানিত।
পরে স্বীয় মুরশিদের নির্দেশে কিশোরগঞ্জের বৌলাই জমিদার বাড়িতে শুভাগমন করে তথায় দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালীন সময়ে বৌলাই জমিদার বাড়ি ছিলো ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। পরবর্তিতে কিশোরগঞ্জের হয়বতনগরের জমিদার মরহুম দেওয়ান মান্নান দাদ খানের অনুরোধে হয়বতনগর তাশরিফ আনেন এবং দাওয়াত ও দীনি কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। অল্প সময়েই সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু এখানে একটি অনৈসলামিক কাজ সংঘটিত হওয়ায় তিনি মর্মাহত হয়ে নিজ বাড়ির দিকে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে তার কিছু ভক্তের অনুরোধে কিশোরগঞ্জ শহরের পুরান থানা মসজিদে সাময়িক অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য নিজ মুরশিদ বরাবর পত্র লিখেন এবং মুরশিদের নির্দেশে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। এখান থেকেই তার কর্মবহুল জীবনের সূত্রপাত ঘটে।
কিশোরগঞ্জবাসীর অনুরোধে তিনি পুরান থানার যে মসজিদটির ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো অত্যন্ত ছোটো। তার আগমনে মুসল্লিদের মধ্যেও অভূতপূর্ব সাড়া পড়লো। তাঁর ইবাদত, জাগরণ এবং শেষ রাতের কান্নাকাটি এতদঞ্চলে এক আশ্চর্যজনক প্রভাব ফেললো। ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুসারীরাও সঠিক পথের সন্ধান পেতে লাগলো। সূচনা হলো এক বিপ্লবের। মাত্র দশ টাকা পুঁজি নিয়েই তিনি পুরান থানা মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। পাল্টে যায় মসজিদের চেহারা,বিশাল এক মসজিদে রূপ নেয় পুরানথানা মসজিদ। এ মসজিদ কেন্দ্রিক এ এলাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তিতে উগ্র হিন্দুরা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মূর্তিসহ মসজিদের সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তওহিদি জনতা মসজিদের মর্যাদা রক্ষার্থে বাধা দেন। ওই সময় পুলিশের গুলিতে একাধিক মুসল্লি শহিদ হন। তখন থেকে এ মসজিদ শহিদী মসজিদ নামে খ্যাতি লাভ করে।
মসজিদকেন্দ্রিক চতুর্দিকে আতহার আলীর রহ. খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। তিনি একটি আধুনিক দীনি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সংকল্প করলেন। নিঃসন্তান এক ব্যাক্তি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা দান করেন এবং নিজ খরচে রেজিষ্ট্রিকরে দেন। অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ তাকে সন্তানের পিতা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন।
১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর প্রধান খলিফা মাওলানা আহমদ আলী খানকে রহ. প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করে জামিয়া ইমদাদিয়া নিয়ে আরেক সংগ্রাম শুরু করেন। তার ইঙ্গিতে হাজারো জনতা মাদরাসা-মসজিদের জন্য জান-মাল কুরবানি দেয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করতে লাগলো। গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক সাড়া পড়লো। মাওলানা আতহার আলীর রহ. কথা বললে দূর-দূরান্তের মানুষও বস্তা ভর্তি ধান, জমির ফসল,বাঁশ সাধ্যমতো দিতে শুরু করলো। যার ফলশ্রুতিতে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতিও পরিলক্ষিত হলো। বিভিন্ন দালান কোঠার কাজ এতো দ্রুতগতিতে শুরু হলো যে, মানুষ অনুমান করতে পারছিলো না এসব কী হচ্ছে!
পাল্টে গেলো কিশোরগঞ্জ শহরের চিত্র। শহরের প্রাণকেন্দ্রে শোভা পাচ্ছিলো বিশাল বিশাল অট্টালিকা। দক্ষিণ পার্শ্বের বিল্ডিংটি ছিলো শহরের মূল সড়ক ঘেঁষে; যা এতো দ্বীর্ঘ ও উঁচু ছিলো যে বহুদিন পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ শহরে এর নজির ছিলো না। চারতলা বিশিষ্ট বিল্ডিং-এর ঠিক মাঝখানে ছিলো তাফসির ক্লাসের জন্য পঞ্চম তলা। তাঁর উদ্দেশ্য যেহেতু শুধু একটি মাদরাসা স্থাপনেই সীমাবদ্ধ ছিলো না তাই অল্প দিনের ব্যবধানেই তিনি এই ছোট্ট মাদরাসাটিকে ‘জামিয়া’ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেন। একটি দীনি মহাকেন্দ্র হিসেবে রূপদিতে ভবনের চেয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর প্রয়োজনও যেহেতু কম নয় তাই তিনি জাহেরি নির্মণকাজের পাশাপাশি বিখ্যাত,স্বনামধন্য, যোগ্যতাসম্পন্ন, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক সংগ্রহে ব্রতী হোন।
যেখানেই কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষকের সন্ধান পেতেন সেখানেই তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাকে জামিয়ায় আনার চেষ্টা করতেন। এমনকি দারুল উলুম দেওবন্দ, জামিয়া ইসলমিয়া করাচীতে অধ্যয়নরত মেধাবী, যোগ্য ছাত্রদেরকে পড়াশুনা শেষে জামিয়াতে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করতেন। তারই ধারাবাহিকতায় সায়্যিদ আবদুল আহাদ কাসেমী রহ.,মাওলানা আশরাফ আলী (কুমিল্লা), মাওলানা কুতুব উদ্দিন (সিলেট), মাওলানা খলিলুর রহমান (বরিশাল), মাওলানা মুহিবক্ষুর রহমান (সিলেট), মাওলানা আবদুর রব (সিলেট), মাওলানা রহমতুল্লাহ (সিলেট), মাওলানা কাজী মু‘তাসিম বিল্লাহ (বর্তমানে মালিবাগ), মাওলানা যুবায়ের, মাওলানা আবদুল হক-এর মতো অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সমাবেশ ঘটেছিলো জামিয়ায়।
জাতীয় জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আজ আমরা যেসব বিষয় নিয়ে ভাবছি মাওলানা আতহার আলী রহ. অর্ধশতাব্দী আগেই সেসব বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং কাজ শুরু করেছিলেন। জামিয়াকে বিভিন্ন বিভাগে সাজিয়েছিলেন। কর্মমূখী শিক্ষার কথা চিন্তা করে লেখাপড়া শেষে ছাত্ররা যেনো আত্মকর্মসংস্থান করতে পারে সেজন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে অনুবাদ ও রচনা বিভাগ। এ বিভাগের অধীনে লেখালেখিতে আগ্রহী শিক্ষকমণ্ডলী ও যোগ্য ছাত্রদেরকে অনুবাদ ও রচনার সুযোগ করে দেয়া হয়।
পৃথক দাওয়াত ও তাবলিগ বিভাগের মাধ্যমে বাংলা এবং উর্দু ভাষায় পৃথক দ্বিমাসিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। বস্ত্রশিল্প বিভাগ। জ্ঞানার্জনের পর শিক্ষার্থীরা যেনো জীবিকার নির্বাহে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠতে পারে সেজন্য এ বিভাগের আওতায় শিক্ষার্থীদেরকে উইভিং, নিটিং, টেইলারিং, বাইন্ডিংসহ বিভিন্ন প্রকারের কাপড় তৈরি ও সেলাই কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।
চিকিৎসা বিভাগ। ১৯৫৯ সালে ইসলামি চিকিৎসার মানোন্নয়নে এ বিভাগ খোলা হয়। পরিসংখ্যান বিভাগ। ভূমি জরিপ (আমিনশীপ) ও বিভিন্ন জরিপ শেখােেনা হতো এ বিভাগের মাধ্যমে। টেলিগ্রাম ও টাইপরাইটিং বিভাগ। তৎকালীন সময়ে যেহেতু কম্পিউটারের অস্তিত্ব ছিলো না তাই এ বিভাগটি আধুনিক বিষয়সমূহের অন্যতম ছিল। ব্যাপক চাহিদা থাকায় এ মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন সহজ ছিলো।
কিন্তু স্বাধীনতার পর কারিগরি ও হস্তশিল্পের অধিকাংশ বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়।
আতহার আলী রহ. শহিদী মসজিদের পাঁচতলা মিনারার একেক তলাকে একেকটি কাজের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। ১৩৬৪(বাংলা) সালের ৮ কার্তিক শহিদী মসজিদের ৫তলা বিশিষ্ট বিশাল মিনারা স্থাপন করা হয়। এর ১ম তলা লাইব্রেরি, ২য় তলা পাঠাগার, ৩য় তলা রচনালয়, ৪র্থ তলা সুধীর আসরের জন্য নির্ধারণ করেন। আজও সেই সুউচ্চ মিনার তাঁর অমর কীর্তির বিমূর্ত প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।
তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উপদেষ্ঠা আবদুল হক ফরিদী বলেছিলেন আমি আমার চাকুরী জীবনে অনেক দীনি মাদরাসা দেখেছি, কিন্তু নিছক দীনি শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক শিল্প কারিগরির সংমিশ্রণ, যা এ প্রতিষ্ঠানে দেখেছি তা অন্য কোথাও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।’
কোনো মতবাদকে প্রতিষ্ঠা গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আজ আমরা পদে পদে তা অনুভব করছি, কিন্তু আতহার আলী রহ. সে প্রয়োজনীয়তা অর্ধশতাব্দী আগেই তা অনুভব করেছেন। তিনি সে সময়ে দৈনিক নাজাত ও সাপ্তাহিক নেজামে ইসলাম নামে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।
শহিদী মসজিদকে কেন্দ্র করে যখন তিনি ধর্মীয় ও সংস্কার কাজে ব্যস্ত ঠিক তখনই পাকিস্তান আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি স্বীয় শিক্ষক আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানীর রহ. নির্দেশে এ মসজিদ থেকেই জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করেন। ১৯৫৩ সালে দেশের খ্যাতনামা আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে ‘নেজামে ইসলাম’ নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এ মসজিদ থেকেই ইসলামি আন্দোলনের ফর্মূলা তৈরি হতো এবং তা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছাতো। এখান থেকেই তিনি প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের এমএনএ এবং এমপি নির্বাচিত হন।
১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষকপ্রজা পার্টি ও নেজামে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ নির্বাচনে নেজামে ইসলাম জাতীয় এ্যসেম্বলীতে ৪টি এবং প্রাদেশিক এ্যসেম্বলীতে ৩৬টি আসন লাভ করে ১৯৫৪-৫৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় এ্যসেম্বলীর স্পীকার ও ১জন মন্ত্রী এবং প্রাদেশিক এ্যসেম্বলীর ৩জন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী নিযুক্ত হন নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে। আতহার আলী রহ. নিজে মন্ত্রী না হয়ে অনেককেই মন্ত্রীত্বের আসনে বসিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে যে ইসলামি ভাবধারা সৃষ্টি হয়েছিলো তা তাঁরই চেষ্টার ফল ছিলো।
তিনি জামিয়ায় বাংলা ভাষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর এতোই জোর দিয়েছিলেন যে, অনেকে ভুল ধারণায় তাঁকে এমন দোষারোপও করছিলেন, তিনি জামিয়াকে কলেজে রূপান্তর করে ফেলেছেন!
১৯৫২ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ কিশোরগঞ্জের হয়বতনগরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ঐতিহাসিক সম্মেলনে যেসব প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছিল তার অন্যতম ছিলো, ‘বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হোক।’শুধু দাবি হিসেবেই সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং করাচীতে পশ্চিম পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি গঠনের সময় পার্টির সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আদর্শগত ঘোষণা সংযোজন করেছিলেন। ফলে এটাই সত্য প্রমাণিত হয় যে,তিনিই ছিলেন অবিভক্ত পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপনকারী প্রথম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।
আতহার আলীকে রহ. আধুনিক কিশোরগঞ্জের স্থপতি বললেও ভুল হবে না। কিশোরগঞ্জ শহরের বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও পাকা রাস্তা ঘাটের ভিত্তিপ্রস্তর তাঁরই অমর কীর্তির নিদর্শন। জামিয়া ইমদাদিয়া পোস্ট অফিসও তার এক কীর্তি।
তৎকালীন সময়ে কওমি মাদরাসার সংখ্যা ছিলো প্রায় ত্রিশ হাজার। তিনিই সর্বপ্রথম মাদরাসাগুলোর ঐক্য, পাঠ্য তালিকায় সমন্বয় ও উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে ব্যাপক তৎপরতা চালান। তাঁর ডাকে ১৯৬২ সালে ‘মু‘তামারে মাদারিসে ইসলামিয়া কওমিয়া,পুর্ব পাকিস্তান’ নামে একটি বোর্ড গঠন করেন। যার সদর দপ্তর ছিলো জামিয়া ইমদাদিয়ায়। সংগঠনটি কিছুদিন পর নানা সমস্যার কারণে কার্যক্রমহীন হয়ে পড়ে। এ স্বপ্নের ফলশ্রুতিতেই পরে দাঁড় হয় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ।
জীবনের শেষভাগে ময়মনসিংহ শহরের চরপাড়া মোড়ের দারুল উলুম নামের ছোট্ট প্রতিষ্ঠানকে খুব অল্প সময়েই জামিয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) স্তরে উন্নীত করে কয়েক কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেন। বিদ্যুৎ বেগে চলে কাজ; কয়েক লক্ষ টাকার কাজ হতে না হতেই চির বিদায়ের ডাক এসে পড়ে তাঁর। ইসলামি শিক্ষা ও আন্দোলনের এ পুরোধা ১৯৭৬-এর ৬ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।
আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া









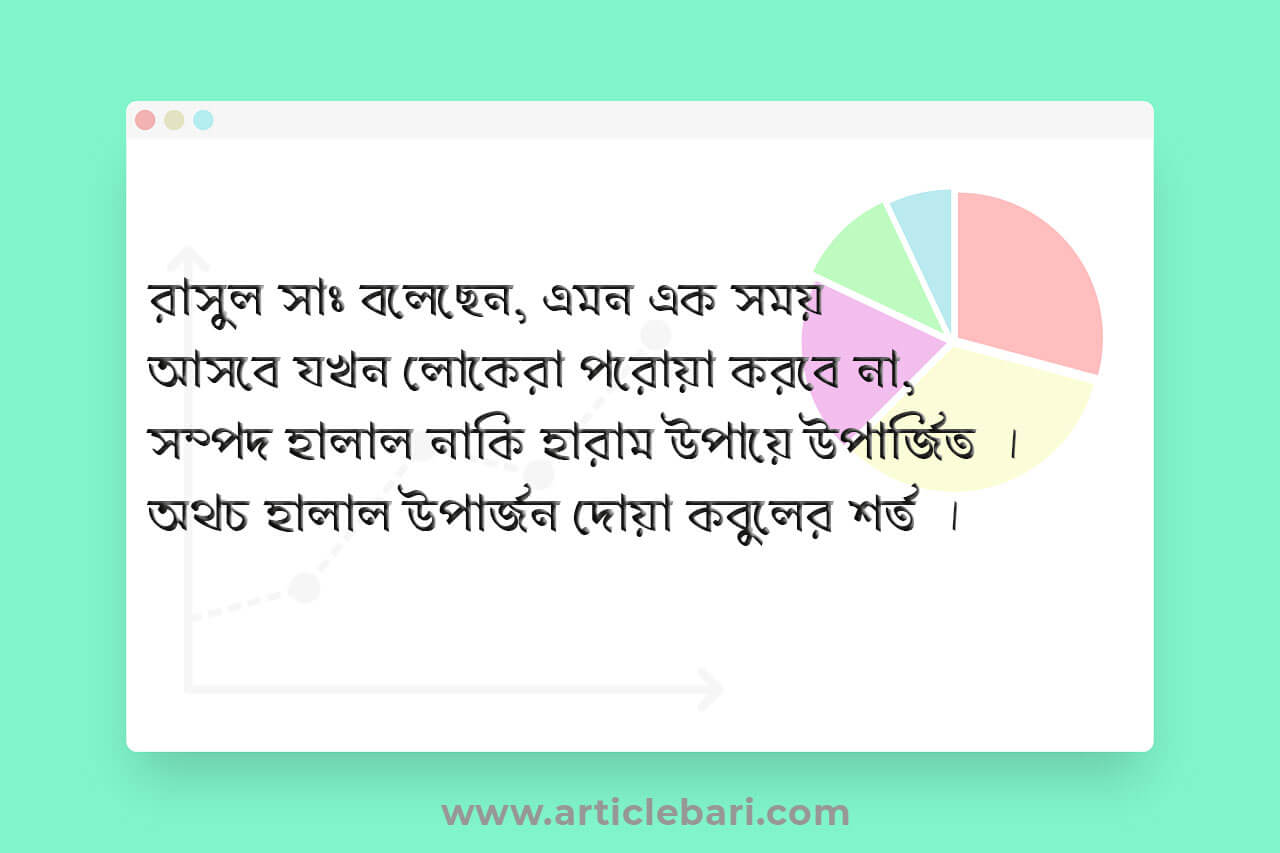 হারাম পথে উপার্জনগুলো কী : সাধারণত যেসব অবৈধ উপায়ে আয়ের পন্থা সমাজে চালু রয়েছে সেসবের মুধ্যে ঘুষ, সুদ, হারাম পণ্যসামগ্রীর ব্যবসা, কালোবাজারী, চোরাকারবারী, নাচ-গান, ফটকবাজারী, সব ধরনের প্রতরণা, পতিতাবৃত্তি, সমস্ত প্রকারের লটারী, জুয়া প্রভৃতিই প্রধান। রাসূল (সা.) এসব হারাম ও অনৈতিক পথে উপার্জন কঠোরভাবে রোধ করেছেন। তৎকালীন সময়েই শুধু নয়, বর্তমান যুগেও অন্য কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এত ব্যাপকভাবে অবৈধ ও অশ্লীল উপায়ে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। একারণেই সেসব মতাদর্শে সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচারের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে।
হারাম পথে উপার্জনগুলো কী : সাধারণত যেসব অবৈধ উপায়ে আয়ের পন্থা সমাজে চালু রয়েছে সেসবের মুধ্যে ঘুষ, সুদ, হারাম পণ্যসামগ্রীর ব্যবসা, কালোবাজারী, চোরাকারবারী, নাচ-গান, ফটকবাজারী, সব ধরনের প্রতরণা, পতিতাবৃত্তি, সমস্ত প্রকারের লটারী, জুয়া প্রভৃতিই প্রধান। রাসূল (সা.) এসব হারাম ও অনৈতিক পথে উপার্জন কঠোরভাবে রোধ করেছেন। তৎকালীন সময়েই শুধু নয়, বর্তমান যুগেও অন্য কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এত ব্যাপকভাবে অবৈধ ও অশ্লীল উপায়ে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। একারণেই সেসব মতাদর্শে সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচারের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে।