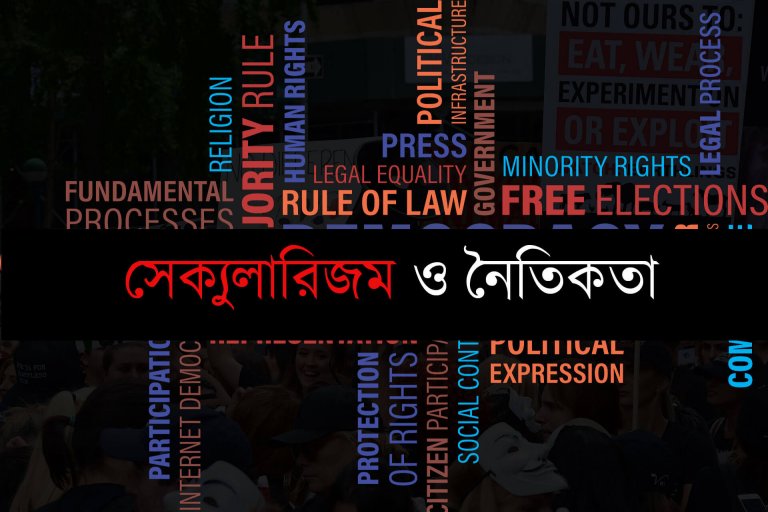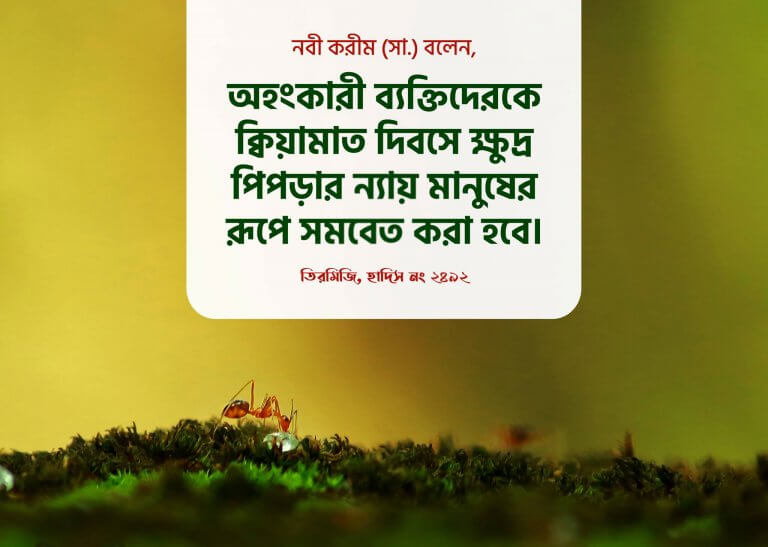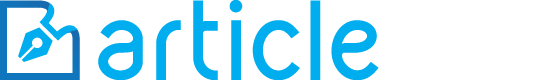মানুষের মর্যাদা
আবহমানকাল ধরে দুনিয়ার ভাগ্য মানুষেরই ভাগ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ দুনিয়ার উন্নতি ও অবনতি, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সম্পর্ক মানুষেরই অস্তিত্বের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তো যদি দুনিয়ায় সঠিক মানব যিন্দা থাকে, আর দুনিয়ার যাবতীয় মূল্যবান জিনিস, ধন-দৌলত ও বিলাস-সামগ্রী শেষ হয়ে যায়, তবুও তেমন উল্লেখযোগ্য কোন বিপর্যয় দেখা দিবে না এবং দুনিয়াটি যে একেবারেই মহাসংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়বে তাও না। বরং মানুষের মতো মানুষের উপস্থিতিই অন্যসব বস্তুর ঘাটতির যথাযথ পরিপূরক। সমস্ত বঞ্চনার প্রতিকার এবং হরেক শ্রান্তির এটিই উত্তম বিনিময় সাব্যস্ত হবে। মানুষ তার কর্ম-তৃপ্তি, উদ্দীপনা এবং শ্রম ও নিপুণতা দিয়ে সেসব লুপ্ত দ্রব্য পুনঃস্থাপন করে দিতে সক্ষম হবে।
এটুকুই নয় শুধু, বরং হারানো সেসব জিনিস অপেক্ষা অত্যধিক কল্যাণকর জিনিস সঞ্চিত করে দেখিয়ে দিতেও প্রয়াসী হবে। যদি দুনিয়ার কোন ক্ষমতাসীনকে এ অধিকার দেওয়া হয় যে, তিনি হয়তো নির্বাচন করবেন দুনিয়া ছেড়ে মানুষকে, নয়তো নির্বাচন করবেন মানুষ ছেড়ে দুনিয়াটিকে (আর তিনি এ নির্বাচনে সুবুদ্ধি ও আল্লাহ প্রদত্ত বিবেকশক্তিকে যথাযথ খাটাবেন) তাহলে এটা অনিবার্য যে, তিনি মানুষকেই গ্রহণ ও নির্বাচন করে নিবেন। এতে তিনি কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয়ের পক্ষপাতী হবেন না। কারণ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র মানুষেরই নিমিত্ত। এ দুনিয়ার মান-মর্যাদা মানুষকে দিয়েই।
এ পৃথিবীতে দুর্ভাগ্য ও অবক্ষয়ের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, বৈষয়িক উপকরণাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর অবর্তমানতা দায়ী নয়। বরং ওসব বৈষয়িক উপকরণাদি ও অস্ত্রশস্ত্রের যথোচিত ও যথাস্থানে ব্যবহার না করারই এই পরিণতি। এ পৃথিবীর সুদীর্ঘ ও ঘটনাপ্রবাহে ভরা ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, এতে যতসব বিপর্যয় আমদানি হয়েছে, সবগুলোরই উৎস মানুষের পথভ্রষ্টতা এবং সুপথ ও মৌল স্বভাব থেকে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়া বৈ কিছু নয়। উপকরণ ও মেশিনাদি তো মানুষের হাতে থাকে বাকহীন ও নিষ্কলঙ্ক সম্বল হিসেবে। ওগুলো মানুষের কথায় চলে এবং মানুষেরই কামনা পূরণ করে থাকে। এ মেশিনাদির যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে বিপদের সময় চলার পথে বোঝা ও কষ্ট বাড়িয়ে তোলে।
মানব প্রকৃতিতে গুপ্ত তথ্য ও রহস্যাবলী
এ বিশাল ভূমণ্ডল তথ্য ও রহস্য এবং নানাবিধ বিস্ময়কর জিনিস এবং অদ্ভুত লীলায় এতোই পরিপূর্ণ, যার রং ও রূপ বিবেককে বিব্রত করে তোলে এবং বিবেক ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।
কিন্তু মানব প্রকৃতির গুপ্ত রহস্যসমূহ, বিস্ময়কর বিষয়াদি এবং এর সম্ভাব্য ফসল এবং লুপ্ত সব প্রতিভা হৃদয়ের প্রসারতা ও গভীরতার সামনে অন্যসবের তো তুলনাই চলে না। মানুষের চিন্তা-শক্তির ঊর্ধ্বারোহণ, মানুষের দিগন্তের সুবিশালতা, মানবাত্মার রোমান্টিকতা, এর মধ্যে পুঞ্জীভূত আশা-আকাঙ্ক্ষা, এর সাহসিকতা ও উচ্চাভিলাষ (যা অসীম ও যা শত জয়, শত আনন্দ, বিশাল রাজ্য ও রাজত্ব এবং প্রাচুর্য ও প্রশান্তির পরও তৃপ্ত হয় না) – এর বিভিন্নমুখী ও বিপরীতধর্মী যে অগণিত ও অসংখ্য প্রক্রিয়া রয়েছে, তা যদি দুনিয়ার অবশিষ্ট তথ্য ও রহস্যসমূহের সাথে পরখ করা হয়, তখন এ সুবিশাল ভূমন্ডল ও সৃষ্টিকুলের তুলনায় সাগরের পাশে এক ফোঁটা পানি কিংবা মুরুভূমির পাশে একটি বালুর কণার মতো বিবেচিত হবে।
সারা বিশ্ব যদিও দেখতে এতো প্রকাণ্ড, কিন্তু মানব মনের প্রসারতা ও গভীরতায় তা নিক্ষেপ করলে এমনিভাবে নিমজ্জিত হয়ে যাবে, যেমনি সাগরের অতলতলে একটি ছোট্ট পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করলে নিমজ্জিত হয়ে যায়।
মানব মনের ঈমানী সুদৃঢ়তা ও অবিচলতার কাছে পাহাড়ের অস্তিত্ব তুচ্ছ। এর জ্বলন্ত প্রেমের আকর্ষণের প্রখর স্ফুলিঙ্গের কাছে আগুনকে মনে হবে শীতল কিংবা ঈষৎ উষ্ণ। আল্লাহ’র ভয়ে কিংবা আর্তের সমবেদনায় অথবা পাপের অনুশোচনায় প্রবাহিত এক ফোঁটা অশ্রু এক সাগরের পানির উপর ছেড়ে দিলে তখন তা নিজ ধারণ ক্ষমতার অপারকতার জন্য মাতম তুলবে। এমনকি নিজ সংকীর্ণতার জন্য শোকাতুর হতে বাধ্য হবে।
মানব চরিত্রে বিরাজমান মাধুর্য, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং প্রেম-প্রকৃতির মায়ামুখর সৌন্দর্যের যদি প্রস্ফুটন ঘটতো, তাহলে এ বসুন্ধরায় রং-বেরঙের বৈচিত্র্য ও মায়াজালের লীলাখেলা ঠাণ্ডা হয়ে যেতো আর সৃষ্টিকূলের রূপ শোভাকে হারিয়ে দিতো। মানুষের অস্তিত্বই নিখিল ধারার লক্ষ্যমণি এবং মহাকাব্য ছন্দের পরম উৎস। বিশ্বস্রস্টার কুদরত লীলার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কুদরতের বাস্তব নকশা মানব জাতি, যে জাতিকে তিনি সুশোভিত করেছেন সর্বোত্তম সৌন্দর্যাকৃতি ও সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্র এবং কাঠামো দিয়ে।
মানুষের তুল্য অন্য কিছুর মূল্য হতে পারে না
পৃথিবীর যাবতীয় খনিজ দ্রব্য, গুপ্ত ধনভাণ্ডার এবং মাল ও দৌলত রাজকীয় মর্যাদা মানবিক সে দৃঢ় প্রত্যয় ও আকিদার তুল্য হতে পারে না, যা দ্বিধা-সংশয়ের বহু ঊর্ধ্বে। তুল্য হতে পারে না সে প্রগাঢ় ভালোবাসার, যা বৈষয়িক লাভ ও উন্নতির দোহাই মানে না। সে আকর্ষণের সমতুল্যও হবে না, যা কারো বিধি-নিষেধকে পরোয়া করে না একটুও। এসব বস্তু মানুষের সেই একনিষ্ঠতার বরাবর হতে পারে না মোটেও, যা স্বার্থপরায়ণতার ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত। মানুষের মহান চরিত্রের সেই মহানুভবতার তুল্য আর কিছু হতে পারে না, যা বিনিময় ও সুযোগ সন্ধানের কালিমা থেকে পবিত্র। হতে পারে না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে নিঃস্বার্থ সেবার সমতুল্য, যা কারো প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের তোয়াক্কা করে না।
মানুষ যদি নিজেকে ঠিক ঠিকভাবে জেনেশুনে তার যথোচিত বিনিময়ের সন্ধানী হয়, তাহলে সমস্ত দুনিয়াবাসী তার সেই বিনিময় পেশ করতে অপারক হয়ে বসবে। যদি তার অস্তিত্ব একটু বিস্তৃতি খুঁজে নেয় এবং নিজ দৃঢ়তা ও নৈপুণ্যের বলগা স্বাধীন করে দেয়, আর এর সাথে সাথে তার স্বভাব-প্রকৃতিকে আপন গতিকে ছুড়ে দেওয়া হয়, তখন এ পৃথিবীটি তার কাছে নেহায়েতই ক্ষুদ্রায়িত হয়ে আসবে এবং সংকীর্ণ হয়ে দীপ্তিহীন বায়ুর পিঞ্জিরায় পরিণত হতে বাধ্য হবে।
পতিত হলে মাত্র এক মুষ্টি মাটি – এ মানব জাতি,
উত্থিত হলে আবার ধরবে না উভয় জাহানেও এ মানব জাতি।
মানব প্রকৃতির গভীরতাকে জরিপ দেওয়া যেমনি দুষ্কর, তেমনি তার শেষ প্রান্তকে অতিক্রম করাও অসম্ভব। তার গুপ্ত রহস্যাবলী আয়ত্তে আনাও যাচ্ছে না, আবার এর তত্ত্বও এবং মূল হাকিকতের সন্ধানটুকুও মিলছে না। এ মানব জাতির বিস্ময়কর এবং বৈচিত্র্যময় যোগ্যতা, জ্ঞান ও সহনশীলতা, ভদ্রতা ও বিনয়ী ভাব, দয়া ও ভালোবাসা, অনুগ্রহ ও দান এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় হতবাক হতে হয়। যতো বড় ধী-শক্তিধরই হোক না কেন, হতবুদ্ধিতার পরিচয় দিতে হয়। অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, যখন চিন্তা করা হয় মানুষের মাঝে দুনিয়ার মোহের প্রতি বিরাগ ও মানুষের ত্যাগ সামর্থ্য, মানুষের আত্মমর্যাদা ও নম্রতা, মাওলার পরিচিতি লাভের উপযোগিতা এবং তার জন্য আত্মত্যাগের বাসনা নিয়ে চিন্তা করলে তো বিব্রত না হয়ে পারা যায় না। এই গোষ্ঠীটির মাঝে পুঞ্জিত জনসেবার প্রেরণা এবং জটিল ও কঠিন নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগ সম্পর্কে যখন ভাবা হয়, তখনও বিস্মিত হতে হয়।
মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতের কৃতিত্ব
মানুষের অস্তিত্বই মূলত যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণকামিতা এবং সৌভাগ্য ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। সমস্ত বৈষম্য ও সংকটের প্রকৃত সমাধানকারী এই মানুষই। এই মানুষের গঠনে যখন বক্রতা চলে আসে আর বিনষ্ট হয়ে উঠে তার কৃষ্টি-কালচার, তখন মানুষের মতো মানুষ মেলা বিরল ও দুর্লভ হয়ে পড়ে। মানুষ তৈরি করার নীতি ও পদ্ধতি তখন আর টিকে থাকে না। মানুষ তৈরি করাই সর্বযুগে নুবওয়াতের প্রধান লক্ষ্যমূল হয়ে আসছে। নবীগণ সবাই নিজ যুগে এ সমস্যাটি নিয়ে জনসমাজে আবির্ভূত হয়েছেন।
মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতের কৃতিত্ব এটুকু যে, এই নবুওয়াতের মাধ্যমে এমন কিছু অতুলনীয় গুণ ও অবর্ণনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ গড়ে উঠেছে, যাদের নজীর ইতিহাসের চোখে কোনদিন ধরা পড়েনি এবং আসেনি এমন অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত সৌর দৃষ্টির সামনে। তারা গ্রথিত মুক্তার মালা, সীসা ঢালা প্রাচীর এবং জামাআত ও সম্প্রদায়ে সুসংগঠিত হলেন, যার ফলশ্রুতিতে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অটুট সূত্র স্থাপন করে ফেললেন। নবুওয়াতে মুহাম্মাদির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুপম কৃতিত্ব আর মহা অলৌকিকতা তো এটিই।
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সুদূর প্রান্ত থেকে মানুষ তৈরি ও মনুষ্যত্বের পুনঃ জাগরণের কাজে হাত দেন, যেখান থেকে আর কোন নবী কিংবা সংস্কারও করতে হয়নি। তারা কেউ এই দায়িত্বে আদিষ্টও হোননি। কেননা, অন্যান্য নবীর সামাজিক পরিবেশ আরবের বর্বরতার যুগ থেকে বহু উচ্চমানের ছিল। তদুপরি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান কাজকে নিয়ে এতখানি উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সফলকাম হলেন, যতখানি অন্য কোন নবীর কর্মধারা পৌঁছেনি।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাশবিকতার চরম সীমা থেকে কর্মনীতি পরিচালনা করলেন। অথচ মানবতার প্রশিক্ষণের সেটিই ছিল প্রাথমিক বিন্দু। তারপর পৌঁছে দিলেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে মনুষ্যত্বের ঊর্ধ্ব শিখরে, যার ঊর্ধ্বে নবুওয়াতের একটি সোপান ছাড়া কোন সোপান আর অবশিষ্ট রয়নি। এই কৃতিত্বের চিরন্তন শিরোপা অর্জন করেন যে মহামানব, তিনিই নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
আসল বাস্তবটি ধারণাতীত চিত্তাকর্ষক
উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি সদস্যই নবুওয়াতের অলৌকিকতার একটি স্বতন্ত্র নিদর্শন এবং নবুওয়াতের শাশ্বত কামিয়াবী এবং মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ। কোন শিল্পী তার তুলির রেখায় কিংবা কল্পনার আকাশে এর চেয়ে সুন্দর কিছু আঁকতে পারে না। পারে না তাদেরকে সেভাবে তুলে ধরতে, যে মনোহর আলোকে তারা বাস্তব ক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল রয়েছেন।
কোন কবির তার প্রাণবন্ত খেয়াল, আনন্দঘন মন ও কবিত্ব শক্তিকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেও মানব সত্তায় বিরাজমান কোমল গুণাবলী, নিখুঁত চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলোর কাল্পনিক নকশা তৈরি করা সম্ভব না। এমনকি সমস্ত সাহিত্যিক সমবেত হলেও মানবতার কোন একটি দিক মাত্রের প্রসারতার বাহ্যিক নমুনা পেশ করার চেষ্টা করা ব্যর্থতার নামান্তর বৈ কিছু নয়।
যারা ছিলেন নবুওয়াতের কোলে লালিত, যারা মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষণ লাভ করে বের হয়েছিলেন, তাদের মজবুত ঈমান, গভীর ইলম আর ন্যায়পরায়ণ মনের কোন তুলনাই হয় না। তাদের জীবন ছিল ভাওতাবাজি, লোক-দেখানো মনোবৃত্তি, মুনাফিকী এবং দাম্ভিকতা থেকে বিলকুল মুক্ত। তাদের আল্লাহ-ভীতি, সাধুতা, পবিত্রতা, আতিথেয়তা এবং অনুগ্রহের ধরণের উদাহরণ অন্যসব উম্মতের মধ্যে বিরল।
এদিকে আবার তারা ছিলেন বীরত্ব ও নিপুণতা, ইবাদাতের অনুপ্রেরণা এবং শাহাদাতের ব্রতে সদাব্রতী। দিন তাদের কাটতো বীরের বেশে এবং রাত কাটিয়ে দিতেন তারা আল্লাহ’র ইবাদাতে। পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের প্রতি বৈরাগ্যের ফলে তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জনদরদ, রাতে প্রজাদের কুশলাদির খবর নেওয়া এবং নিজের আরামকে হারাম করে জনগণকে শান্তি পৌঁছানোর অভিব্যক্তিতে তাদের তুলনা বিরল।
জীবনের বিভিন্ন ধাপে ও বিভিন্ন ময়দানে নিষ্ঠাবান মনীষা
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাওয়াত ও রিসালাতের মাধ্যমে তৈরি করলেন এমন এমন মনীষা, যারা আল্লাহ’র উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপনকারী, তার গ্রেফতার সম্পর্কে নিতান্তই ভীত, দ্বীনদার, আমানতদার, দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্যদাতা এবং জড়বস্তুর রঙ্গমঞ্চের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। জড় বস্তুকে তারা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে কাবু করে নিতেন।
তাদের প্রাণভরা আস্থা এটি ছিল যে, দুনিয়াকে তাদেরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখিরাতের জন্য। এজন্যই ব্যবসা ক্ষেত্রে তারা পরিচিত হতেন নিষ্ঠাবান ও আমানতদার ব্যবসায়ী হিসেবে। অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তারা পরিচিত হতেন ভদ্র ও মেহনতী মানুষ হিসেবে। শুভাকাঙ্ক্ষী শাসনকর্তা ও কঠোর পরিশ্রমীরূপে তারা চিহ্নিত হতেন যখন কোন অঞ্চলের শাসনের দায়িত্ব নিতেন। তাদের হাতে যখন অর্থ ভাণ্ডার আসতো, তখন অতুলনীয় করুনা ও সমবেদনার সাথে এর সদ্ব্যবহার করে থাকতেন।
ন্যায়পরায়ণতায় অনুরাগী ও বাস্তবানুরাগী হিসেবে তারা প্রমাণিত হতেন, যখন তারা বিচার ও আদালতের এজলাসে সমাসীন হতেন। তারা কোথাও গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত হলে একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত হিসেবে আখ্যায়িত হতেন। নেতৃত্বের অঙ্গনে তারা বিনয়ী, অন্তরঙ্গ এবং সমবেদনা প্রদর্শনকারী নেতারূপে প্রতীয়মান হতেন। জনসাধারণের অর্থ-তহবিলের দায়িত্ব পেলে তারা ভক্ষক না হয়ে বুদ্ধিমান রক্ষক হিসেবে খ্যাত হতেন।
যেসব বুনিয়াদি জিনিস দিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো
উল্লিখিত আদর্শসমূহের ইট দ্বারা ইসলামী সমাজের প্রাচীরটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। সেসব জিনিসকে নির্ভর করেই ইসলামী হুকুমাত একদিন দাঁড়িয়েছিলো। সে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রকারান্তে সে সকল মনীষীরই চারিত্রিক ও মানসিক অবস্থার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাদেরই ন্যায় তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজটি ছিল আমানতের পথিকৃৎ। ইহকালের উপর পরকালকে প্রাধান্য প্রদানকারী ছিল সেই সমাজটি। বস্তু কর্তৃক প্রভাবান্বিত না হয়ে বস্তুর প্রশাসক হতেন তারা।
এ সমাজের নেতৃত্বে এক ব্যবসায়ীর সততা ও আমানত, এক নিঃস্বের সারল্য ও দৈন্য, এক শাসনকর্তার পরিশ্রম ও শুভ কামনা, একজন ধনবানের বদান্যতা ও হিত কামনা এবং বিচারকর্তার ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার যৌথ মিশ্রণ বিদ্যমান ছিল। এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় একজন গভর্নরের একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা, একজন নেতার বিনয়ী ভাব ও দয়া, একজন কৃতজ্ঞ সেচ্ছাসেবকের সার্বিক প্রয়াস এবং একজন আমানতদার প্রহরীর অতন্দ্রপ্রহরা ও সতর্ক দৃষ্টির সমাবেশ ঘটেছিলো।
রাষ্ট্রটি ছিল দাওয়াত ও হিদায়াতের পতাকাবাহী। এ রাষ্ট্র আকিদার জগতকে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের উপর প্রাধান্য দিতো। এ রাষ্ট্র অর্থ সংগ্রহ ও ট্যাক্স তহশীলের উপর জনগণকে হিদায়াত দান ও সুপথ প্রদর্শনকে প্রাধান্য দিয়ে সে সমাজের প্রভাব ও প্রচলন এবং তার রাষ্ট্রীয় প্রভাবে জনজীবনে ঈমান, সুকর্ম, সততা, একনিষ্ঠতা, জিহাদ ও ইজতেহাদ, লেনদেন, ন্যায় ও সাম্য এবং পারস্পরিক ইনসাফ কায়েমের দৃশ্যই একমাত্র গোচরীভূত হতো।
পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার যাচাইয়ে নিষ্ঠাবানদের সফলকামিতা
সেসব নিষ্ঠাবানই এমন এমন কঠিন পরীক্ষা ও যাচাইয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, যেসব পরীক্ষায় মানবিক দুর্বল দিকগুলো আর গুপ্ত ব্যাধিসমূহের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে পারে না। অথচ তারা সে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার জ্বলন্ত চুল্লী থেকে অকৃত্রিম ও নির্ভেজাল হীরকের মতো বের হয়ে এসেছেন। তার মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেজাল কিংবা অন্য কিছুর মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়নি। সমস্ত নাযুক পরিস্থিতিতে তারা ঈমানী শক্তি, অভিপ্রেত ক্ষমতা আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশিক্ষণের আদর্শকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। নিজ সততা, দায়িত্ববোধ, আমানত, আত্মনির্ভরশীলতা আর আত্মবিসর্জনের বুলন্দ নমুনা তারা পেশ করতেন। পরবর্তী যুগের মনোবিজ্ঞানী, চরিত্র বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক ও প্রকৃতিবিদগণের ধারণাতীত নজীর স্থাপন করে গেছেন তারা।
সেসব নাযুক পরিস্থিতিগুলো হতে বেশী নাযুক পরিস্থিতি হচ্ছে আমীর ও শাসকের পদটি। তিনি পৃথিবীর কারো কাছে জবাবদিহি করার নন, নেই তার পিছনে কোন প্রকার গুপ্তচর নিয়োজিত, তাকে কোন কমিটি কিংবা আদালতের সম্মুখীন হওয়ারও নেই – অথচ তিনি নিজের জন্য অনেক অনেক বৈধ জিনিসের ব্যাপারেও সংযমী থাকতেন। নিজের ব্যক্তিগত সম্পদের দিক থেকেও উদাসীনতা প্রদর্শন করতেন। এমনকি সামান্য সম্পদেরও ধার ধারতেন না তিনি। অথচ সেগুলোর ব্যবহার শরীয়তের পক্ষ থেকে একান্তই বৈধ। সাধারণ সমাজেও তা ব্যবহার্য আর সর্বযুগেই তা তুচ্ছ ও নগণ্যের ফিরিস্তিতে শামিল রয়েছে।
শাসকদের দুনিয়া সম্পর্কে অনীহা ভাব ও তাদের সারল্য
এ প্রেক্ষিতে সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে, খলিফাতুল মুসলিমীন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু’র মহীয়সী পত্নীর একদিন মিষ্টান্ন খাওয়ার অভিপ্রায়ের ঘটনাটি। এজন্য তিনি তার দৈনন্দিন খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে রেখে সঞ্চয় করেছিলেন। সিদ্দীকে আকবর ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত হলে তিনি সে সঞ্চিত টাকাগুলো বায়তুলমালে জমা তো দিয়ে দিলেনই, সাথে সাথে দৈনন্দিনের নির্ধারিত ভাতা থেকে সে পরিমাণ কেটে কমিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এ কথা বোঝার আর বাকি নেই যে, এ পরিমাণ ভাতা এ যাবত অতিরিক্ত আসছিলো। আর বললেন, নির্ধারিত ভাতার চেয়ে কমেও তো আবু বকরের জীবন যাপন সম্ভব। মুসলমানদের বায়তুল মাল তো এজন্য নয় যে, এর দ্বারা প্রশাসকের পরিবার-পরিজন বিলাসবহুল জীবন যাপনের সুযোগ গ্রহণ করবে। আর আহারে-বিহারে তারা অত্যধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময়ী হয়ে পড়বে।
এ প্রসঙ্গে খিলাফতে রাশিদার শাসনামলের একটি সত্য ছবি আমি তুলে ধরছি। আর এটি হছে তদানীন্তন বৃহত্তর সাম্রাজ্যের শৌর্যশালী একজন প্রশাসকের সরকারী সফরকে কেন্দ্র করে। তা ছিল এমন একজন প্রতাপশালী প্রশাসকের সফর, যার নাম শোনামাত্র জনমনে কম্পন সৃষ্টি হতো তারা বর্ণনাকারী সফরসঙ্গী ছিলেন বিধায়। তার প্রত্যক্ষ বর্ণনাটিই তার সাহিত্যের অলংকারে অলংকৃত করে যেভাবে বর্ণনা দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আমি ঠিক সেভাবে পেশ করার চেষ্টা করবো। ইবনে কাসির বর্ণনা করেন –
“উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে একটি মেটে রঙের উটের উপর সওয়ার হয়ে রওয়ানা দিলেন। খুব রৌদ্র তাপ। তার মাথায় নেই লৌহ-শিরস্ত্রাণ, নেই পাগড়ি। উটের পিঠের হাওদার উপর বসে বসে তিনি পা দুটো দুদিকে ঝুলিয়ে রাখছেন। পা দুটো রাখার জন্য দুটো রেকাবও ছিল না। উটের উপর ছিল একটি মোটা পশমী কাপড়। মাঝেমধ্যে উট থেকে নেমে তিনি সেটি বিছাতেন। তৃণলতায় ভরা তার চামড়ার অথবা পশমের একটি পুটলি ছিল। যখন উটের উপর থাকতেন তখন সেটিতে হেলান দিতেন, নেমে সেটি দিয়ে বালিশের কাজ করতেন। পরনের জামাটি ছিল খুবই মোটা। সুতি বস্ত্র। তাও কাঁধের তলদেশ দিয়ে ছেঁড়া ছিল।
খলিফার আদেশক্রমে লোকজন তথাকার সর্দারকে ডাকতে গেলো। জুলুমুসকে ডাকতে গেলো। তারপর খলীফা তার পরনের জামাটি ধুয়ে ছেঁড়া জায়গায় একটি তালি লাগিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং ধার হিসেবে ক্ষণিকের জন্য একটি কাপড় কিংবা জামার ব্যবস্থা করতে বললেন। একটি রেশমী জামা উপস্থাপিত করা হলো। তিনি দেখামাত্র বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন – এটা কি ? লোকজন বললেন- রেশম। তিনি জানতে চাইলেন যে, রেশম কি জিনিস ? লোকজন তা বুঝিয়ে দিলে তিনি পরনের জামাটি খুলে গোসল করে নিলেন। ইত্যবসরে তার তালি দেওয়া জামাটি হাযির করা হলে তিনি রেশমী জামাটি খুলে সেটিই পরিধান করে নিলেন।
উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু’র খেদমতে জুলুমুস পরামর্শ হিসেবে আবেদন জানালো যে, আপনি আরবের বাদশাহ। এখানকার লোকজনের মধ্যে উটের কোন গুরুত্ব নেই। এই হেতু আপনি মর্যাদাপূর্ণ পোশাক পড়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে নিলে রোমানদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করবে। এ আবেদনের প্রেক্ষাপটে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন – আমরা সেই জাতি, আল্লাহ পাক যাদের সম্মান বৃদ্ধির মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন একমাত্র ইসলামকেই, তাই আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সম্মান মাধ্যমকে উপেক্ষা করে অন্য কিছুকে মাধ্যম হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি না মোটেই।
একটি ঘোড়া আনা হলো। তিনি তার চাদরটি রেখে দিলেন ঘোড়াটির উপর। লাগাম লাগালেন না আর রেকাবও সংযোগ করলেন না, বরং এমনিতেই সওয়ার হয়ে গেলেন ঘোড়াটির উপর। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তিনি বলে উঠলেন – থামো, থামো, আমি এর আগে কাউকে আর শয়তানের উপর সওয়ার হতে দেখিনি। এরপর তার উটটি আনা হলে তিনি সেটাতেই সওয়ার হয়ে গেলেন।” (১)
ইতিহাসবেত্তা তাবারীও অনুরূপ একটি ঘটনা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু’র একটি ভ্রমণ বিবরণীতে বর্ণনা করেছেন –
“একসময় উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ভ্রমণে বের হলেন। স্থলাভিষিক্ত করে রেখে গেলেন তিনি মদীনায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’কে। কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামও তার সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি লোহিত সাগরের তীরে ইবিল্লার দিকে যাচ্ছিলেন। ইবিল্লার সন্নিকটে এসে পাশ কেটে তিনি সামনে বেড়ে গেলেন এবং গোলামকে তার পিছনে রেখে দিলেন। এরপর তিনি ইস্তিঞ্জা করে নিলেন। ইস্তিঞ্জা হাতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি গোলামের সওয়ারীটির উপর সওয়ার হয়ে গেলেন। নিজের সওয়ারীটি দিয়ে দিলেন তার গোলামকে। এরপর সেখানকার জনগণের প্রথম দলটি এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো – আমিরুল মুমিনীন কোথায়? উত্তরের তিনি বললেন – তিনি তোমাদের সামনেই। অতএব, জনগণ সামনে বেড়ে গেলেন। ইবিল্লা পৌঁছে খলীফা বললেন – আমিরুল মুমিনীন ইবিল্লা পৌঁছল, যদ্দরুন জনগণ তাকে চিনে নিতে আর ভুল করলো না এবং সবাই তার দিকে ঝুঁকে পড়লো।” (২)
মানবতার আদর্শ নমুনা
খুলাফায়ে রাশিদা ও সাহাবায়ে কিরামগণের জীবনচরিতে দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ভাব, নম্রতা, কুরবানী, সমবেদনা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিপুণতা, প্রজ্ঞা ও সততার উজ্জ্বল আদর্শ এতো অধিক পাওয়া যায়, যেগুলোকে কোন ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, মনোবিজ্ঞানী বা চরিত্র বিশেষজ্ঞ যদি একত্র করে গুছিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র অংকনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যই মানব মণ্ডলে তা একটি অনুপম আদর্শ ও নিখুঁত ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিভাত হবে। পরিণত হবে তা দিয়ে মানবতার মহাজাগরণের অ্যালবাম। মানবতার বিশ্বজনীন প্রদর্শনীতে তা আদৃত হবে এক অপূর্ব শোভার নিদর্শন হিসেবে।
কিন্তু পরিতাপের সাথে বলতে হয়, আমরা সে মনোনীত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জামাআতটির পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ গুণাবলী ও চিত্র কোন গ্রন্থে খুঁজে পাচ্ছি না। তা অবশ্য তাদের জীবনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুকোমল সংস্পর্শে ও সুস্নিগ্ধ দীক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। তা থেকে মাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলো, কিছু সাহিত্য সুষমামণ্ডিত রচনা এবং চরিত্র চিত্রণ গ্রন্থাবলীতে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। কেননা, আরববাসীগণ আবহমান কাল ধরে স্বীয় পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, শিল্প নিপুণতা এবং যথোচিত ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে শিরোপা অর্জন করে আসছে। তাদের সে সাহিত্য-প্রজ্ঞা ও শিল্প-নিপুণতার বদৌলতেই আমরা নববী সংস্পর্শের প্রভাব ও ফলাফল এবং সফলতা ও অনুপমতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আঁচ করতে সক্ষম হচ্ছি এবং সে সুপ্রতিষ্ঠিত মহতী সমাজটির নমুনা অবলোকন করার সুযোগ পাচ্ছি।
তাদের সে আদর্শমাখা সমাজটিকে দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য নিয়ে দৃষ্টিলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। তার মধ্যে একটি দৃশ্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’কে নিয়ে, যা ভাব ও সাহিত্যিকতার নিরিখে অতীব রসালো। সে চিত্রটি তার প্রভাব ও তাৎপর্য বিচারে বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক সাহিত্য জগতের এক অনুপম উপজীব্য হওয়ার দাবী রাখে।
একদিন আমীরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র একজন ঘনিষ্ঠ সহচর যিরার ইবন যামরাকে আবেদন জানালেন, তিনি যেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। যিরার ইবন যামরার খুবই কাছে থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সোহবত নেওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। আমীরের আবেদন অনুযায়ী যিরার বলতে লাগলেন –
“আল্লাহ’র শপথ, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন, সুঠাম দেহের অধিকারী একজন বীর কেশরী। তার ফয়সালা যে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো। ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতো তার ফয়সালা। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র প্রতিটি কাজ থেকে জ্ঞানের প্রস্রবণ উৎসরিত হতো। দুনিয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি ছিল তার নিঃস্পৃহতা। রাতে একাকী অন্ধকারে তিনি বেশী বেশী সময় কাটাতেন।
আমি আল্লাহ’র শপথ করে বলছি, অত্যধিক আহাজারী ও কান্নাকাটি, অবর্ণনীয় চিন্তা-সাধনাই ছিল তার সার্বক্ষণিক ও অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি তার হাতের তালু নিজের দিকে ফিরিয়ে সম্বোধন করতেন নিজেই নিজেকে। অতীত কর্মের হিসাবও নিতেন নিজেই। মোটা কাপড় ও সাধারণ পানাহার পছন্দ করতেন। আমাদের মধ্যে থাকতেন তিনি আমাদেরই মতো হয়ে। আবার যখন কোন কথা জানতে চাইতাম, তা প্রশান্তচিত্তে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। আমরা তার কাছে আসলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতেন। তাকে আমরা দাওয়াত করলে চলে আসতেন অকুণ্ঠ চিত্তে। কিন্তু তার নজিরবিহীন অন্তরঙ্গতা ও বিনয়ী ভাব এবং সারল্য সত্ত্বেও আমরা তার প্রতি সৃষ্টি ভীতিমাখা শ্রদ্ধার ফলে বেশী কিছু বলার হিম্মত হারিয়ে ফেলতাম। এমনকি আমাদের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলার সূচনা করার সাহসটুকুও হতো না। মৃদু হাসিটুকু যখন দিতেন তিনি, মুক্তামালার মতো দাঁতগুলো চকচক করতো। দ্বীনদারদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সহায়-সম্বলহারাদের সমবেদনা প্রদর্শনই ছিল তার জীবনের মৌল আদর্শ। যতটুকু প্রতাপশালী ব্যক্তিই হোক না কেন, তাকে দিয়ে কোন প্রকার অন্যায়ের পক্ষপাতিত্বের আশাটুকু করতো না। কোন আর্ত ও দুর্বল মানুষ তার ন্যায়পরায়ণতা থেকে বঞ্চিত ও বিমুখ হতো না।
আমি আবারো আল্লাহ’র শপথ করে বলছি, আমি অনেক সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, রাত শেষ হতে চলেছে, তারকারাজি অস্তপ্রায়, তিনি তখন তার দাড়িগুলো ধরে মসজিদের মিহরাবে সর্পে দংশিত মানুষের মতো অস্থির ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছেন কিংবা নিতান্তই বিষাদগ্রস্ত হয়ে কাঁদছেন।
আমি তাকে এ কথা বলতে শুনতাম – হে দুনিয়া, তুই কি আমাকে যাবতীয় বিপর্যয়ের লক্ষ্যস্থল নির্ণীত করতে চাস ? আমাকে আকৃষ্ট করার জন্যই কি তোর এসব অভিমান ও ছলনা ? দূর হো, তুই দূর হো। তোর প্রতারণা আমার এখানে না, অন্যখানে। আমি তোকে এমনভাবে তালাক দিয়েছি যে, তোর দিকে প্রত্যাবর্তন করা আর সম্ভব না। তোকে নিয়ে জীবনকাল নেহায়েতই সাময়িক। তোকে দিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অকিঞ্চিৎ। অথচ পরিণাম তার কতোই না ধ্বংসাত্মক। আহ ! চলার পথের পাথেয় এতো সামান্য, অথচ ভ্রমণ কতো দীর্ঘ, পরন্তু পথ কতোই কণ্টকাকীর্ণ।”
প্রথম ইসলামী সমাজ
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত সে সমাজটি মানব ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ হিসেবে নন্দিত ও স্বীকৃত। এটি একমাত্র তারই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুপম তারবিয়াতের ফসল। সে সমাজটি যেমনি ছিল হৃদয়গ্রাহী তেমনি মানবিক সমস্ত গুণের সঞ্চিত ভান্ডার। সে সমাজটির সঠিক রূপরেখাটি ফুটে উঠেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বিশ্বস্ত সহচর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু’র একটি বর্ণিত হাদিস দিয়ে, যা নিতান্তই সাহিত্য রসালো, সংক্ষিপ্ত, তাৎপর্য, বিশালত্ব, গাম্ভীর্য এবং ভাববোধক শব্দে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেন, “সাহাবায়ে কিরাম অপরাপরের মাঝে ছিলেন পূত হৃদয়ের অধিকারী, গভীর প্রজ্ঞাময়। তাদের জীবনে লৌকিকতা বা কৃত্রিমতা খুবই কম পরিলক্ষিত হতো। তারা ছিলেন সেসব মনীষী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় সান্নিধ্য লাভের এবং দ্বীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ ও মদদের নিমত্ত স্বয়ং আল্লাহ পাক যাদেরকে নির্বাচন করেছিলেন।” (৩)
যখন সেই মহতী সমাজটিকে অন্য কোন সমাজের সাথে তুলনা করা হবে, তো সমষ্টিগতভাবে সেটির পাল্লা বহু ভারী প্রতীয়মান হবে। আর তাদের দুর্বলতার দিক (যা থেকে সৃষ্টিমাত্রই মুক্ত নয়) এদের গুণাবলী ও আদর্শাবলীর তুলনায় একেবারেই নগণ্য ও অধর্তব্য সাব্যস্ত হবে। তাদের চরিত্র মাধুরীর দৃষ্টান্ত তো মানব ইতিহাসে বিরল। এই প্রেক্ষিতে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ’র সাহিত্য অলংকারমন্ডিত সুদৃঢ় বাণীটি প্রণিধানযোগ্য মনে করি –
“সাহাবায়ে কিরামগণই ছিলেন এই উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কেননা, হিদায়াত ও দ্বীনের পথে উম্মতের মধ্যে তাদের চেয়ে অগ্রগামী অন্য কেউ হয়ে উঠেনি। মতভেদ ও মতানৈক্য থেকে তারাই তুলনামূলক বেশী মুক্ত ছিলেন। আর যদি কোথাও তাদের সাথে কোন ত্রুটির সংযুক্তি ঘটেছে, তা অন্যদের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। অনুরূপ এ উম্মতের ত্রুটিগুলো অন্য সমাজগুলোর নিরিখে হিসাব করলে তা তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় বলে বিবেচিত হবে। তা দেখে যারা সাহাবায়ে কিরামগণ সম্পর্কে ভিত্তিহীন অপপ্রচারে মত্ত হয়েছে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেন তারা ফটিকের মতো শুভ্র কাপড়ের একটি তিলককে প্রকট করে দেখানোর অপচেষ্টা করছে। তারা অন্যান্য সমাজের কালো কাপড়গুলো দেখছে না, যার ভিতরে শুভ্রতার বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। এ ধরেনর সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত জুলুম ও অজ্ঞতার পরিণতি বৈ কিছু নয়।” (৪)
পরবর্তী বংশধরগণের উপর মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতের প্রভাব
নববী দাওয়াত, তালীম ও সুমহান আদর্শ, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের জীবন-চরিতের রূপ-রঙে উপস্থাপন করেছিলেন, তা শুধু সে যমানার জন্যই সীমিত ছিল তা নয়, বরং পরবর্তী উত্তরসূরিদেরকেও শিক্ষাদানের দিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুপ্রাণিত করেছেন।
কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সনাতন আদর্শ সকল দেশ এবং সকল পরিবেশের জন্য শাশ্বত আদর্শ। তাই তা চলার পথের দীপ্ত প্রদীপ এবং চিরন্তন পথিকৃৎ। আর এজন্যই এমন জিনিস তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত সমাজটিতে শুধু সীমাবদ্ধ থাকার নয়। বরং তা সেই জ্যোতিষ্মান সূর্যের মতো যার আলো ও তাপে প্রতিটি যুগে প্রতিটি স্থানে ফসল ও ফল-ফলাদি পরিপক্বতা লাভ করছে। এটি এমন শাশ্বত সূর্য, যেটি আপন সৌরমণ্ডলে অবস্থান করছে বটে, কিন্তু তার মৃদু সোনালি মাখা সঞ্জীবনী কিরণ এ বসুন্ধরাকে প্রতিনিয়ত প্রেরণ করছে। কাছে হোক কিংবা দূরে থাকুক, প্রতিটি প্রাণী তা থেকে লাভ করছে সজীবতা।
আল্লাহ তাআলা আর আখিরাতের উপর ঈমান আনার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত , আল্লাহ’র মেহেরবানীর প্রতি তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐকান্তিকতা, তার অসন্তুষ্টি ও গ্রেফতারীর ভয়, প্রতিদান ও সওয়াবের প্রত্যাশা, জাহান্নামের ভীতি, জান্নাতের প্রেরণা, পার্থিব জিনিসের প্রতি নিঃস্পৃহতা, আখিরাতের পাথেয়র অনুসন্ধান, অত্যধিক সারল্য, নিজ ও নিজ সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া, অনাত্মীয়ের জন্য ত্যাগ, তাদেরকে আত্মীয়দের চেয়েও নিকটতম ভাবার মানসিকতা ইত্যাদি এক বিশ্বজয়ী সার্বজনীন শিক্ষণীয় পাঠ্যসূচী হিসেবে গণ্য। শুধু তাই নয়, বরং জিহাদ, উৎসর্গীকরণ ও আত্মবিসর্জনের মতো জীবন-পরীক্ষায় একান্ত আপনজনদেরকে সামনে বাড়িয়ে দেওয়া বিভিন্ন চরিত্র মাধুরী ও সূক্ষ্ম অনুভূতি চালিত উজ্জীবন বিশ্বজনীন প্রশিক্ষণই বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচ্য।
মোটকথা, তা দিয়ে পরবর্তীকালে বংশ পরম্পরায় মানব সন্তানগণ আদর্শবান হচ্ছিলো। উলামা, নেতৃবর্গ, রাজা-বাদশা, শাসক-প্রশাসক, আবিদ-জাহিদ সকলেই এ ফোয়ারা থেকে স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়ে আসছে। চরিত্র ও মানবতার প্রথম সবক নিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে এ শিক্ষা পাদপীঠ থেকে, যার ফলে স্বীয় চরিত্র মাধুরীর উৎকর্ষ, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আমানতদারী, বিলাস-সামগ্রী, ধনাগারের চাবি, প্রশাসন ভাব এবং সমাজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে নিয়ন্ত্রিত থাকা সত্ত্বেও তারা দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন। তারা আল্লাহ’র ইবাদাতে যুগের পথিকৃৎ ছিলেন।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে দীক্ষিত মনীষীগণ স্থান ও কালের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও নবুওয়াতের ফসল, ইসলামী দাওয়াতের ফল এবং মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতেরই কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের নিদর্শন হয়ে রয়েছেন। এদের চরিত্রে যে আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, এসব তো নবুওয়াতে মুহাম্মাদিরই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিচ্ছবি। এই আকিদা-বিশ্বাস ও চরিত্র বিকাশে তাদের পিতা-মাতা, পরিবেশ এবং নিজস্ব মেধার তেমন কোন ভুমিকা নেই। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে দাওয়াত ও তালীম না হলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও অনুশীলনের প্রেরণা জাগ্রত হয়ে ইসলামের অবদানে তারা ধন্য না হলে, হয়তো তারা আকিদাগত দিক দিয়ে হতো মূর্তিপূজারী, হতো হিংস্র পশুর তুল্য। তাওহীদ যদি না হতো, আল্লাহ-ভীতি আসতো না। দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও ত্যাগ না হলে ক্ষমা ও উদারতার মহানুভবতা তারা পেতো না। কোন মহৎ অনুপ্রেরণাও আসতো না, ফলে তাদের চরিত্র মাধুর্যও দেখা যেতো না।
বিশ্বজনীন ও শাশ্বত মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শ নিকেতনের কিছু খ্যাতিমান শিষ্য এবং তাদের সুমধুর চরিত্র ও জীবনের কিছু দৃষ্টান্ত সেই আদর্শ শিক্ষা নিকেতন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন একজনকেই সামনে রাখুন, যিনি ইসলামের মূল দোলনা তথা আরব উপদ্বীপ থেকে সুদূরবর্তী এক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রিসালাতের সময়কাল পেরিয়ে যাওয়ার বহু পরে এ মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। জন্ম ও বংশগত দিক দিয়ে যার রক্তমাংস ছিল অনারবীয়। সে মনীষী সুলতান সালাহুদ্দীন কুর্দি আজমী।
ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নামে বিখ্যাত। ষষ্ঠ হিজরিতে তার আবির্ভাব। তার সম্পর্কে তারই একজন বিশ্বস্ত সহচর (সেক্রেটারি) ইবন শাদ্দাদের বক্তব্য নিন্মরূপঃ
“পক্ষান্তরে তার শাসনামলে দেশ কি উন্নতি লাভ করেনি ? তদুপরি মৃত্যুকালে রেখে যান তিনি সর্বমোট মাত্র সাতচল্লিশটি নার্সেরী রৌপ্য মুদ্রা আর একটি স্বর্ণ মুদ্রা। ওজনের দিক দিয়ে তা কতটুকু ছিল তা আমার জানা নেই। আমি তাকে একবার বায়তুল মুকাদ্দাসে বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের মাঝখানে দেখেছিলাম। তিনি তখন দিমাশক যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেসব প্রতিনিধি দলকে দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না তার কোষাগারে। আমি তখন এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করছিলাম। পরিশেষে তিনি বায়তুল মালের কিছু সামগ্রী বিক্রি করে সব প্রতিনিধি দলের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। একটি রৌপ্য মুদ্রাও অবশিষ্ট রইলো না।
প্রাচুর্যের সময় যেভাবে তিনি প্রাণ খুলে দান করতেন, দৈন্যের সময়ও ঠিক অনুরূপ উদারচিত্তে তা অব্যাহত রাখতেন। যদ্দরুন তার কোষাধ্যাক্ষগণ অনেক সময় তার অজান্তে কিছু মাল লুকিয়ে রাখতেন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ সুলতান যখনই কোন দ্রব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতেন, তখনই তা চেয়ে নিতেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন – এমনও কিছু মানুষ আছে, যারা ধন-সম্পদকে মাটির মতো ভেবে থাকে। উক্তিটি দিয়ে যেন তিনি নিজেকেই উদ্দেশ্য করছিলেন। সর্বদাই তিনি সাহায্য প্রার্থীর আশারও ঊর্ধ্বে দান করে থাকতেন।” (৫)
এমন একজন মহান সম্রাট, যার সাম্রাজ্য সিরিয়ার উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিনে নওবা মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহধাম ছেড়ে চলেছেন, অথচ তার নিজের কোষাগারে দাফন-কাফনের পয়সাটুকুও ছিল না।
ইবন শাদ্দাদ বলেন –
“এরপর তাকে গোসল দেওয়া ও কাফনের প্রস্তুতি চলছিল যখন, তখন আমাদের তার ব্যবস্থা এভাবে গ্রহণ করতে হয়েছিলো যে, সাধারণ ও তুচ্ছ জিনিস পর্যন্ত ধার করে আনতে হয়েছিলো। এমনকি কবরে রাখার জন্য ঘাসের আঁটি পর্যন্ত যোগাড় করতে হয়েছিলো ধার করে। যোহরের নামাযের পর একটি সাধারণ খাটে আবৃত করে তার জানাযা আনা হলো। কাফনের কাপড় সবটুকুও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কাযী ফাযিল।” (৬)
সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি সম্পর্কে ইউরোপীয় জীবনীকার লেনপুন (Stanely Lanepool) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “সালাহুদ্দিন” (পৃষ্ঠা ২০৫) এ লিপিবদ্ধ করেন, “সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ভদ্রতা ও সুপরিসর মানসিকতার অবগতি সম্পর্কে একটি ঘটনার অবতারণই যথেষ্ট, যা ঘটেছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের সময়। এ বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ও পুনরুদ্ধারের সময় তিনি খৃষ্টান শত্রুদের যে অতুলনীয় সদাচরণ দেখিয়েছিলেন, তা ছাড়া যদি আর কোন কিছুই তার সম্পর্কে না জানা যায়, তবুও এটুকুই এটা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হবে যে, তা ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মহত্ত্ব, শৌর্যবীর্য ও পৌরষের শ্রেষ্ঠত্বে তার সমকক্ষ সেখানে আর কেউ ছিল না। বরং এসব ক্ষেত্রে যেন তিনি সর্বকালের মানুষের শীর্ষে অবস্থান করেছেন।”
এ মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতের প্রভাব নিজ শক্তি, প্রেরণা ও সম্ভাবনাময় পরিপূর্ণতা নিয়ে প্রতিটি যুগে সক্রিয় রয়েছে। এমনকি এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে সেসব ইসলামী রাষ্ট্র থেকে সুদূরে এক প্রান্তে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহেও। প্রকাশ পেয়েছে সেসব নতুন নতুন সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের মাঝেও, যারা ইসলামের প্রথম সারির মনীষীদের সাথে ভাষা, বংশ ও শিল্পগত দিক দিয়ে আদৌ সম্পৃক্ত ছিল না। তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে এমন হয়েছিলো যে, তারা প্রথম ইসলামী দাওয়াতদাতা কিংবা আধ্যাত্মিক পীরের হাতে মুসলমান হতেন।
পরে তাদেরই বংশে কোন বাদশাহ কিংবা শাহী মর্যাদার এমন আল্লাহ-ভীরু কামিল ওয়ালীর আবির্ভাব ঘটতো, যার মধ্যে আল্লাহ-প্রীতি, তাকওয়া, ইনসাফ, সাম্য, সমবেদনা ও সহানুভূতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, আল্লাহ’র তুষ্টি ও একনিষ্ঠতা, সততা ও সরলতার এমন প্রতীক সাব্যস্ত হতো, যা অন্য সমাজের হিবর, রাহিব, পোপ এবং পাদরীদের মধ্যেও হতো না। তাদের রাজা ও মহারাজাদের তো প্রশ্নই উঠে না।
আমি উপমহাদেশের দীর্ঘ ইসলামী ইতিহাসে এ জাতীয় সমৃদ্ধ বহু ঘটনার এমন একটি উদাহরণ পেশ করছি, যেটির অভূতপূর্ব আকর্ষণ, অকৃত্রিমতা যতদিনই অতিবাহিত হোক না কেন, যতবারই তা শোনা যাক না কেন, হ্রাস পায়নি কিঞ্চিৎও।
গুজরাটের বাদশাহ মুজাফফর হালীম (মৃত্যু ৯৩২ হিজরি) আর তার সমসাময়িক মান্ডোর শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ খিলজীর মাঝখানে বহুদিন যাবত রাজনৈতিক মতপার্থক্য চলছিলো। সুলতান খিলজী তার রণচাতুর্যের দরুন উপর্যুপরি আক্রমণ অব্যাহত রাখতেন। ফলে সুলতান মুজাফফর হালীমকেও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো। ভাগ্যের পরিহাস, কালের পট পরিবর্তন হলো, পতন আসতে লাগলো মাহমুদের শৌর্য-বীর্যে।
পরিশেষে পরাক্রমশালী সুলতান মাহমুদকে একজন আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে তার পুরনো ঘোর শত্রুর দ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হলো। কেননা তার ওয়াযীর মুন্ডলী রায় তার রাজ্যে জবর দখল করে বসেছে।
সুলতান মাহমুদ সাহায্য প্রার্থনার জন্য সুলতান মুজাফফর হালীমের সহানুভূতি ও সাহায্য কামনা ছাড়া ইসলামী মর্যাদাবোধের দৃষ্টিতে অন্য কোথাও তার আশ্রয়ের স্থল খুঁজে পেলো না। তাই তিনি পরিশেষে সুলতান মুজাফফরকেই স্বীয় সাহায্য-সহানুভূতি, মদদ ও সহযোগিতার যোগ্য পাত্র মনে করলেন। জাহিলী সংকীর্ণতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিছুতেই সম্ভব হতো না, পারতো না কোন জড়বাদী দর্শনের অনুসারী এভাবে শত্রুকেই যথার্থ আশ্রয়স্থল বলে ভাবতে। আবার এদিকে সুলতান মুজাফফর হালীম সে সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। একটু কটাক্ষও তিনি করলেন না প্রাণের শত্রুকে। বরং একমাত্র আল্লাহ’র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আর নাফস ও শয়তানের ভেলকী নস্যাৎ করার এটিকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিলেন।
দেরী না করে সুলতান মুজাফফর এক বিরাট সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে মান্ডোর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি যে তার শত্রু রাষ্ট্রের (রাজনৈতিক) সমস্যাকে নিজের রাষ্ট্রের সমস্যার তুল্য ভেবেছিলেন তাই নয়, বরং তার চেয়েও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আযাদীর সংরক্ষণ ও ইসলামের শান-শওকতের পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের রাষ্ট্রের আযাদী ও নিরাপত্তাকে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। ওদিকে কাফির সেনা ও শিরক শক্তিগুলো তাদের মিত্র রাষ্ট্র মান্ডোর সাহায্যের উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্রে একত্রিত হতে শুরু করলো। ফলে সংঘটিত হয় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সে যুদ্ধে শত শত মৃতদেহের বিরাট স্তুপ হলো। রাজপথগুলোয় প্রবাহিত হলো রক্তধারা। পরিশেষে সুলতান মুজাফফরেরই বিজয় হলো, শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ করলো। রাজপুত রাজাদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী রাজপুত ও সম্রাজ্ঞীগণ জহরব্রত পালনের প্রাচীন রীতি সমাপন করলো। অবশেষে এ রাষ্ট্র ইসলামী শাসনের আওতাভুক্ত হলো।
এখানে মানবিক ভদ্রতা ও ইসলামী আদর্শের আরো একটি উত্তম নমুনা প্রতিভাত হচ্ছে। তা হচ্ছে এই – সুলতান মুজাফফর হালীমের কিছু সামরিক উপদেষ্টা তাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এ মনোরম উর্বর ভূমিটি বাদশাহ যেন হাতছাড়া না করেন। কেননা, সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য, দুর্ভেদ্য দুর্গে আর পরিপূর্ণ কোষাগারে এই দেশটির তুলনা উপমহাদেশে আর একটি নেই। যা দুর্বল ও পথভ্রষ্ট বাদশার অদূরদর্শিতার কারণে জীর্ণ হয়ে আসছিলো। তাদের যৌক্তিকতা ছিল এই যে, বাদশাহ যেহেতু এই মান্ডোকে নব অভিযানের মাধ্যমে জয় করলেন, সুতরাং তিনি-ই এই বিজিত রাষ্ট্রের অধিকারী। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্র তো শক্তি ও বিজয়েরই ফসল। আর বিজিত দেশকে সাধারনত বিজেতারই হক ও অধিকার ভাবা হয়।
সুলতান মুজাফফর হালীম সেনানায়কদের এ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হলে সাথে সাথে তিনি সুলতান মাহমুদকে নির্দেশ দিলেন যে, তার সৈনিকদের কাউকে যেন নগরীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়। সুলতান মাহমুদ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাদশাহ মুজাফফরকে মাত্র কিছুক্ষণ সময় দুর্গে অবস্থান করে বিশ্রাম নেওয়া আর গোসল ইত্যাদি করার জন্য আহবান জানালে সুলতান মুজাফফর শুকরিয়ার সাথে তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। তার সৈনিকদেরকে আহমদাবাদ আর নিজ নিজ ঠিকানায় প্রত্যাবর্তনের জন্য হুকুম দিলেন। আর সুলতান মাহমুদকে বললেন, আমি এই দেশে এসেছি একমাত্র আল্লাহ’র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমত্ত, তার সওয়াবের আশায় আর তার হুকুম পালন করার উদ্দেশ্যে।
“….. তারা যদি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তোমাদের জন্য অপরিহার্য হবে তাদের সাহায্য করা …..” (সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৭২)
“একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের ভাই। এক ভাই অপর ভাইকে শত্রুর কাছে সোপর্দ করতে পারে না আর অপমানিত করতেও পারে না।” (হাদিস)
উপরোক্ত উক্তি দুটো পেশ করে সুলতান মুজাফফর বললেন, এখন আমার নিয়ত পুরা হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাকে, আপনাকে আর ইসলামকে সফল করেছেন। আমি আমার সঙ্গী-সাথীদের থেকে এমন কিছু উক্তি ও যুক্তি পেয়েছি, যেগুলোয় আমি কান দিলে আমার সব আমল বিনষ্ট হতো, জিহাদ বরবাদ হতো। মূলত এ ব্যাপারে আমার কোন অবদান নেই। অবদান তো সবটুকু আপনার। আমাকে এ শুভ কাজের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করেছেন তো আপনি। আপনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এখন আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করেছি। আমি আমার আমলকে মূল্যহীন করতে চাইনি। ভালোর সাথে মন্দের ভেজাল দিতে আমি রাযী নই।
বাদশার এ ভাবগম্ভীর বক্তব্য শুনে তার বিজয়ী সেনাদল আনন্দ হিল্লোলে মেতে উঠলো। আহমদাবাদের দিকে ইচ্ছার বলগাকে ফিরিয়ে দিলেন নিপুণ অশ্বারোহীগণ। একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলে গেলেন তারা নিজ দেশে।
সুলতান মুজাফফর মান্ডো বিজয়ের সময় যখন বিজয়ীর বেশে সসম্ভ্রমে নগরীর দিকে প্রবেশ করছিলেন, তখন সুলতান মাহমুদ তার মনোরঞ্জনের জন্য তাকে ধনাগার ও প্রাচুর্যগুলো পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। মান্ডোর প্রতিটি জিনিস ছিল নেহায়েত চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যময়। নগরীটি এক দীর্ঘকাল ব্যাপী সৌন্দর্য, সজীবতা, সম্পদ ও স্থপতি, রূপসী দাসী ও মহিলাদের মীনা বাজারের খ্যাতি লাভ করে আসছিলো। অথচ সুলতান মুজাফফর মাথা নিচু করে সেসব থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে পথ অতিক্রম করে আসছিলেন। বিজয়ী নেতার অভিনন্দন জ্ঞাপনার্থে হাসিমুখে প্রতীক্ষারত দাস-দাসী ও সেচ্ছাসেবী ছাউনি অতিক্রমকালে সুলতান মাহমুদ তার লাজুক ও সংকুচিত সহযাত্রী সুলতান মুজাফফরকে নিবেদন জানালেন – জনাবে আলী, ব্যাপার কি ? আপনি যে মাথা উঠাচ্ছেন না আর এমন নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলো একটু লক্ষ্যও করছেন না ?
সুলতান মুজাফফর বললেন – আমার জন্য তা জায়েয না। আল্লাহ পাক বলেছেন –
“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে …….”(সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ৩০)
সুলতান মাহমুদ বললেন – এরা তো আমারই দাসী, এদিকে আমি আপনার এমন একজন গোলাম, যাকে আপনার অফুরন্ত করুনা আজীবনের জন্য কিনে নিয়েছে। তাই এরা নীতিগতভাবেই আপনার দাস-দাসী।
কিন্তু সুলতান মুজাফফরকে এ যুক্তি স্বস্তি যোগাতে ব্যর্থ হয়। তার নিশ্চিত প্রত্যয় এই ছিল যে, আল্লাহ পাক যা হারাম করেছেন, তা অন্য কেউ হালাল করার নেই। (৭)
এভাবে আল্লাহ-প্রেমিক মুত্তাকী বাদশাহ তার ভদ্রতা, অন্তরের পবিত্রতা, ইসলামের প্রতি মজবুত আকর্ষণ আর ইসলামী চরিত্রের বুলন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এগুলো কৃত্রিম ছিল না। বরং এগুলোতেই তার প্রকৃতি গড়ে উঠেছিলো। নিক্তিতেই গড়া ছিল তার দৈনন্দিন জীবন প্রণালী। অথচ একজন আদর্শের দিশারী বাদশার বংশধারা দুই তিন পুরুষ পূর্বে গিয়ে অমুসলিম হিন্দু বংশের পেশাধারী নর্তকীদের সাথে মিশে যায়। এমন একটি বংশের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন ইসলামের সম্মানে বিভূষিত হলেন, এক বিরাট সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনে সফল হয়ে গেলেন। ইতিহাসবেত্তাগণ তার পিতামহের উপরে গিয়ে ইসলামী নাম আর খুঁজে পাচ্ছেন না। ফিরোজশাহ তুগলকের শাসনকালে তারা অষ্টম হিজরীতে ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাই এর পূর্বে গিয়ে ইসলামী নাম না এসে ভারতীয় নাম আসতে থাকে। তাই তাদের ইসলামী বংশের ধারাবাহিক পরিচিতি শত তল্লাশী চালিয়েও মিলেনি।
এ অতুলনীয় ভদ্রতা ও আল্লাহ-ভীতি তিনি পেলেন একমাত্র মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শের শিক্ষানিকেতন থেকেই। তিনি সে শিক্ষানিকেতনের একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন মাত্র। তিনি ইসলামের নিয়ামত এবং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসান ও অবদানকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সদ্ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। দ্বীনের সাথে তার সম্পৃক্তি নিতান্তই আন্তরিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল।
যে শাশ্বত ও মুবারক শিক্ষা নিকেতনের কৃতিত্ব সার্বজনীন ও সর্বকালীন
এ সুষমামণ্ডিত ও নয়নাভিরাম শিক্ষা পাদপীঠ থেকে যে কতো কৃতী সন্তান সারা বিশ্বে কারণে আওয়াল সাহাবা যুগ, তাবেয়ীনদের যুগ আর পরবর্তী যুগসমূহে বের হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেসব খ্যাতিমান সন্তানদের কতোই না কৃতিত্ব, বিজয় সম্মান ও শ্রদ্ধাঞ্জলী বসুন্ধরার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে।
এ পাদপীঠের প্রশিক্ষণ ও এর প্রতিষ্ঠার প্রভাব কখনো প্রতিফলিত হয়েছে মহাবীর তারেকের দুঃসাহসিকতায়, মুহাম্মাদ ইবন কাসিমের অসীম বীরত্বে এবং মুসা ইবন নাসীরের আজেয় মনোবলে। আবার কখনো তা প্রতিফলিত হয়েছে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈ’র মেধা ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিতে। কখনো তা ধরা দিয়েছে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ইমাম মালিকের দৃঢ়তা ও অটলতার আকৃতিতে। আবার কখনো এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নুরুদ্দীন যঙ্গী’র দয়া-দাক্ষিণ্যের ধরণ নিয়ে। আবার কখনো সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি’র অধ্যবসায় ও সাধনার রঙে রঞ্জিত হয়ে তা প্রদর্শিত হয়েছে। ইমাম গাযযালির দর্শনের বেশে সামনে এসেছে কখনো, আবদুল কাদির জিলানির সংস্কার ও আধ্যাত্মিকতার রক্তে রঞ্জিত হয়ে এসেছে কখনো।
মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা নিকেতনের সে প্রভাব ইবন জাওযীর মাধ্যমে কখনো বিকশিত হয়েছে, আবার কখনো তা মুহাম্মাদ ফাতিহের তরবারী সেজেছে। সুলতান মাহমুদ গযনভীর রণস্পৃহা নিয়ে কখনো চমকিত হয়েছে, কখনো নিজামুদ্দীন আউলিয়ার করুনা ও বিনয়রূপে তা প্রমাণিত হয়েছে। একবার রূপ ধারণ করেছে ফিরোয শাহ খিলজীর উচ্চ মানসিকতায় ভূষিত হয়ে আবার তা ইমাম তাইমিয়ার সুগভীর ইলমী প্রজ্ঞার ধাঁচে ধরা দিয়েছে। সামনে এসেছে তা কখনো শেরশাহ সূরীর দূরদৃষ্টির বেশে, কখনো সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের লৌহ মনোবলের বেশে।
এ মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষাগারেও তার প্রতিষ্ঠাতার প্রেরণা প্রতিফলিত হয়েছে কোন কোন সময় শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মুনীরার মারিফাত ও দর্শনে, কখনো মুজাদ্দিদে আলফেসানীর তীর্যক লেখনী ও অভিযানে। আবার তা কোন কোন সময় প্রস্ফুটিত হয়েছে আবদুল ওয়াহহাব নাজদীর দাওয়াতের কলিতে। কখনো শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনরূপে প্রকাশিত হয়েছে, আবার কখনো উত্তরসূরি দাওয়াতদাতা উলামায়ে রাব্বানীয়ীনদের অনুপম খিদমতের চমক নিয়ে বিকশিত হয়েছে।
এসব খ্যাতিমান মনীষীর ইলমী ও আমলী খিদমতের সূত্রধারা সেই মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষাগারের প্রশিক্ষণের সাথে জুড়ে রয়েছে, যা ছিল এ ধারার প্রাথমিক স্বর্ণযুগ। আর এটিই ছিল সে যুগ, যে যুগে মানবতার সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভাবনাগুলো উৎসরিত হচ্ছিলো। আর তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমেই সূচিত হয়। সে যুগেই ওসব যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করার মতো যোগ্য পাত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো।
মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ শিক্ষানিকেতন কালের শত অবজ্ঞা এবং জনগণের জানাবিধ অনীহা সত্ত্বেও ইতিহাসে কতো নজীরবিহীন ব্যক্তিবর্গকে সৃষ্টি করে আসছে আল্লাহ’র মহিমায় নিজ ফসল ও _ দ্বারা তারা মানবতার শুন্য কোটাটিকে পরিপূর্ণ করে আসছে। এ অনুপম শিক্ষাগারটি সেসকল একনিষ্ঠ নেতৃবর্গ আর রাব্বানী আলিমকুলের বদৌলতে অব্যাহত রেখেছে মানবতা ও ন্যায়পরায়ণতা অনুসন্ধানের পথটুকু। যারা কুরআনের ভাষায় বিঘোষিত হয়েছে –
“…… ঈমানদারদের সামনে তারা নিতান্তই বিনয়ী, কাফিরদের বেলায় বজ্রকঠোর; আল্লাহ’র পথে জিহাদ করে, অথচ তারা বিদ্রুপকারীদের কিঞ্চিৎও পরোয়া করে না ……” (সূরাহ আল-মাইদাহ, ৫ : ৫৪)
এদিকে এ গায়েবী আওয়াজে প্রতিনিয়ত শ্রুত হচ্ছে –
“…… আর যদি এ কুরআনের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে আমি এর জন্য এমন এক সমাজকে নির্ধারণ করবো, যারা তা অস্বীকার করবে না।” (সূরাহ আল আনআম, ৬ : ৮৯)
©???? The Greatest Nation