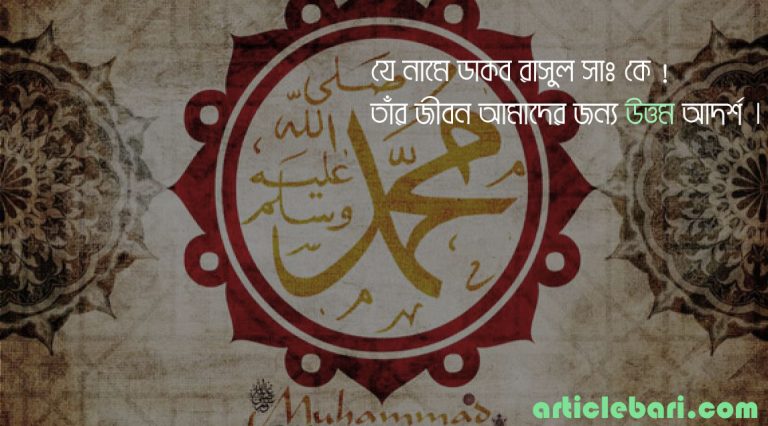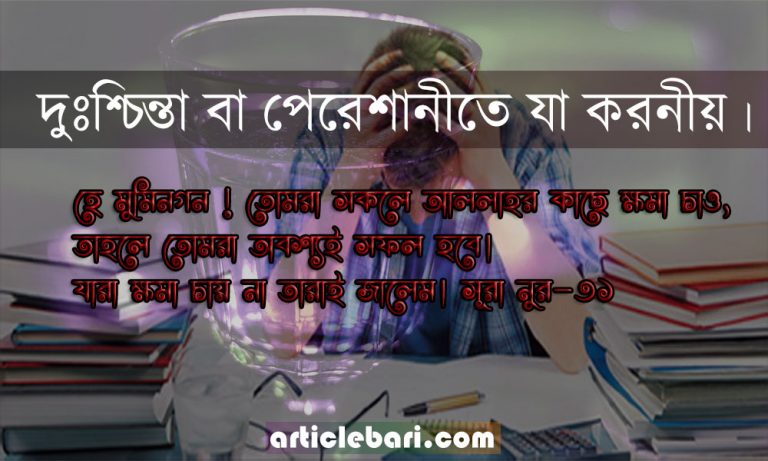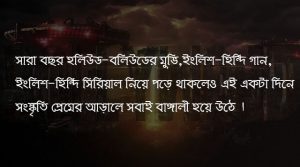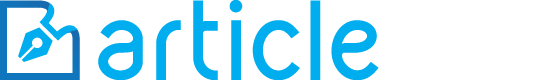চৈত্র্যের শেষদিকের উত্তাপে বাহিরে বের হওয়াও যেন কষ্টসাধ্য। সেই উত্তাপ এই অঞ্চলের কতিপয় বুড়োবুড়িদেরকে জীবনের নতুন আরেকটি বছরে প্রবেশ করার কথা মনে করিয়ে দেয়; কারণ সত্যিই তারা এখনও বাংলায় বছর গোণে। আর বাকিরা ইংরেজি এপ্রিল মাসের তারিখ গুণে গুণে নতুন বছর আগমনের হিসেব কষে, সারাবছর কোনো খবর না থাকলেও অন্তত নতুন বছরের শুরুর দিনটিতে নিজ সংস্কৃতির, নিজ ভাষার ক্যালেন্ডারের হক আদায় করা চাই। অন্যান্য নববর্ষগুলোর মত এখানকার নববর্ষের শুরুরও একটি নাম রয়েছে – পহেলা বৈশাখ।
উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যে বিষয়াদিগুলোতে দরদ থাকে কম, অনাদর আর অবহেলা থাকে বেশি সেগুলোর মধ্যেও ‘মুসলিম’ পরিচয়টা সবকিছুকে হার মানিয়েছে। সেই অনাদর আর অবহেলায় তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্ধারণ করে দেওয়া ফিতরাতের ভাঙ্গাগড়া করা হয়েছে। আর পরিশষে তা অন্যরূপ ধারণ করে বসেছে… যার কেন্দ্র হয়েছে খেয়াল-খুশি আর কামনা-বাসনা – যে করেই হোক একটু আনন্দ পাওয়া, একটু সুন্দর সময় কাটানো অথবা পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসার নিয়মমাফিক ব্যস্ততাকে একটু ভুলে থাকার প্রয়াস – এসবের জন্য এমন সুযোগ খুব কমই আসে।
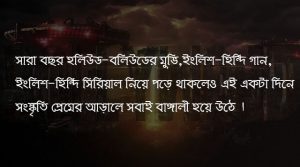
এর উপর সাথে রয়েছে সংস্কৃতিপ্রেম দেখানোর অযুহাত। এমনকি সারাবছর হলিউড-বলিউডের মুভি, ইংলিশ আর হিন্দি গান, ইংলিশ সিরিজ আর হিন্দি সিরিয়াল নিয়ে পড়ে থাকলেও এই একটা দিনে সংস্কৃতিপ্রেমের অযুহাতের আড়ালে সবাই পাক্কা বাঙ্গালী হয়ে উঠে। ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’ নাকি ‘মুখোশের আড়ালে হিন্দু সংস্কৃতি’ সেই ইতিহাসের কথা কারও মনে থাকে না। সেক্যুলার চেতনাবাজ আর হলুদ মিডিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় মূর্তিপূজার আর কুসংস্কারের সংস্কৃতি অসাম্প্রদায়িকের আখ্যা পেয়ে যায়। আর ইসলামের সমস্ত বিষয়ে কলা বিভাগের বিজ্ঞানীদের আস্ফালন দেখা গেলেও এই অবৈজ্ঞানিক বৈশাখ পালনে তাদের কোনো মাথাব্যাথা দেখা যায় না। বরং এই সময়ে তারা তাদের কলা জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে মূর্তি আর মুখোশ তৈরিতে ব্যস্ত হয়।
মিথ্যার নাম অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি
ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলত না। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করতে হত। খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন।
সম্রাটের আদেশ মতে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবি হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে “বঙ্গাব্দ” বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়।
[সিরাজুল ইসলাম, সম্পাদক (জানুয়ারি ২০০৩)। “পহেলা বৈশাখ”। বাংলাপিডিয়া (বাংলা ভাষায়)। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ।]
মুশরিকদের দ্বারা প্রভাবিত শাসক আকবরের রূহে শির্কী সংস্কৃতি গুলে ছিল। তার উদ্ভাবিত জগাখিচুড়ী ধর্ম ‘দ্বীন-ই-ইলাহী’র মত সব ধর্মের অংশগ্রহণে একটি উৎসব হওয়া তার কাম্য ছিল। বৈশাখের অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে তার আকাংক্ষিত মিশ্র উৎসব। এতে মূলত উৎফুল্ল হয় তার হিন্দু স্ত্রী ও হিন্দু প্রজারা। উল্লেখ্য, আকবরের প্রায় পাঁচ শতাধিক স্ত্রী ছিল আর তাদের এক বিরাট অংশ ছিল হিন্দু।
বাংলা বর্ষের মাসগুলোর নামকরণ হয়েছে হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের নামানুসারে। আবার সেই নামকরণগুলো হয়েছিল বিভিন্ন দেবদেবী বা পৌরাণিক চরিত্র থেকে। যেমন ‘বৈশাখ’ মাসেরই নামকরণ করা হয়েছে ‘বিশাখা’ থেকে, যার ঋগ্বেদিক নাম হল ইন্দ্র, আগুনের দেব ইত্যাদি।
আর বর্তমানে যে রকম ঢাকঢোল পিটিয়ে, বাদ্যবাজনা বাজিয়ে বা শোভাযাত্রা করে বৈশাখের প্রথম দিনকে আমন্ত্রন জানানো হয়, পেছনে ফিরে তাকালে আমরা এসব কোনকিছুই দেখতে পাবো না। বস্তুত আধুনিক নববর্ষ উদযাপনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ সালে। যে বছর প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে পহেলা বৈশাখে ‘হোম কীর্ত্তণ’ আর পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সালেও অনুরূপ কর্মকান্ডের উল্লেখ পাওযা যায়। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ সনের আগে ঘটা করে পহেলা বৈশাখ পালনের রীতি তেমন একটা জনপ্রিয় হয় নি। এই হল হাজার(!) বছরের সংস্কৃতি।
অতীতে পহেলা বৈশাখে প্রধান কাজ ছিল সারা বছরের দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ, খাজনা আদায়, শুল্ক পরিশোধ করা ইত্যাদি। এদিনে হিন্দু জমিদাররা নিজ নিজ প্রজাদের মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়ণ করতো এবং এ অনুষ্ঠানকে বলা হতো “পূণ্যাহ”।
চৈত্র্যের শেষ দিনে, বাঙ্গালী সনাতন ধর্মালম্বীরা ‘চৈত্রসংক্রান্তি’র উৎসব পালন করতো। এটি তাদের একটি ধর্মীয় উৎসব। এদিন তারা ঘরদুয়ার ধুয়েমুছে পরিস্কার করে সারা বছরের আবর্জনা দূর করতো। এখনও পুরনো ঢাকার হিন্দুরা এদিন ঝাড়ু হাতে ওঝা সেজে ভূতপ্রেত, অমঙ্গল বা অনিষ্টকে দূর করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় এ উৎসবকে কেন্দ্র করেই পহেলা বৈশাখে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা হতো, যা এখনও হয়।
সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পুজোর জন্য ঈশা খাঁর সোনারগাঁওয়ে সমবেত হতো এবং এখনও হয়ে থাকে। এবং পূজার উদ্দেশ্যে ব্যতিক্রমী এক মেলা মেলার আয়োজন করেছিল। সেখান থেকেই পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন হয়।
কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাট মন্দিরে, আসাম, বঙ্গ, কেরল, মনিপুর, নেপাল, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিল নাড়ু এবং ত্রিপুরার জায়গায় এখনো পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে পূজা অর্চনা হয়ে থাকে অনেকে পুরানিক অর্থে দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের স্ত্রী ঋতু দেবিকে সন্তুষ্ট করার আশায় তারা পুজা করে থাকে। তাদের বিশ্বাস এতে তাদের ফসল ফলাদি ভাল হয়।
শিখদের বসন্তের ফসল তোলাকালীন আর তাদের সৌর নববর্ষের উৎসবের নাম ‘ভৈসাখী’। ১৬৯৯ সালে গোবিন্দ সিং এই উৎসবের আধুনিক ধারার প্রচলন করলেও প্রাচীনকাল থেকেই ফলন ভাল হওয়ার আশায় শিখরা এই উৎসব পালন করতো।
পহেলা বৈশাখের অন্যতম আকর্ষণ মঙ্গল শোভাযাত্রা। হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনের মূর্তি যেমন: কার্তিকের বাহন ময়ূর, স্বরস্বতীর বাহন হাঁস, লক্ষীর বাহন পেঁচা ইত্যাদি সহ বিভিন্ন রাক্ষস-খোক্ষস ও জীবজন্তুর বিশাল মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখে সকালে এই শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। ১৯৮৯ সাল থেকে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা পহেলা বৈশাখের উৎসবের একটি অন্যতম আকর্ষণ।
এছাড়া, দিনের প্রথম প্রত্যুষে নতুন সূর্যকে যেভাবে সুরের মূর্ছনায় বরণ করে নেয়া হয়, সেটাও হাজার বছরে পূর্বের সূর্যপূজারী বা প্রকৃতিপূজারী সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণ। বৈশাখের প্রথম দিনে নতুন সূর্যের কাছে প্রকৃতিপূজারীদের মতোই নিজেদের অমঙ্গল থেকে রক্ষার জন্য সূর্যের নিকট প্রার্থনা করা হয়।
সুতরাং, পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে মেলা, মঙ্গল শোভাযাত্রা কিংবা নতুন বছরকে স্বাগত জানানো প্রতিটি আনুষ্ঠানিকতাই পুরোপুরি সনাতন ধর্মালম্বীদের বিভিন্ন বিশ্বাস ও কর্মকান্ড থেকে উদ্ভূত। পহেলা বৈশাখের আনুষ্ঠানিকতাও তাই কোনভাবেই অসাম্প্রদায়িক নয়, বরং সর্বাংশে সাম্প্রদায়িক।
তাই সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে বৈশাখ উদযাপনের জন্য এর বিরোধিতাকারীদের ‘গোঁড়া’, ‘ধর্মান্ধ’ বলে দিয়ে নিজের কাছে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে মোটেই ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। ‘গোঁড়া’, ‘ধর্মান্ধ’ এসব বলে পাশ কাটিয়ে গেলেও ওই আখিরাতমুখী গোঁড়া মানুষগুলো যে আসলে তাদের মুসলিম ভাইবোনদের জান্নাত চায় বলেই এত কথা খরচ করে, এত কাঠখড় পোড়ায় সেকথা অল্পই অনুধাবণ করতে পারে। একদিনের যে আনন্দটুকুর জন্য জাহান্নামে শতবছর পুড়তে হতে পারে সেই আনন্দের চেয়ে ঠুনকো আর যে কিছুই হতে পারে না।
পহেলা বৈশাখে মোটামোটি পাঁচ ধরনের মুসলিম দেখা যায় –
১) যারা সত্যিই বিশ্বাস করে যে নতুন বছরের নতুন দিন ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ করলে বা ভাল সময় কাটালে সারাটা বছর ভাল কাটবে বা সারা বছর ভাল কাটলেও কাটতে পারে।
২) যারা উপরের এসব বিশ্বাস করে না, কিন্তু এমনিতেই একটু ঘুরে বেড়িয়ে বা স্রেফ একটু ভাল সময় কাটানোর বের হয়।
৩) যারা মৌলিক আকিদাহ সঠিকই পোষণ করে এবং বৈশাখী কার্যকলাপে সরাসরি অংশ নেয় না। তবে কেবলই বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ঘরে বসে পারিবারিকভাবে বৈশাখ পালন জায়েজ মনে করে বা এভাবে বৈশাখ পালনকে ইসলামবিরোধী কিছু মনে করে না; অথবা এভাবে বৈশাখ পালন অসমর্থন করে না।
৪) যারা সত্যিই কোনো প্রয়োজনীয় কাজে বৈশাখের দিন বের হয়।
৫) যারা প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবরদস্তিপূর্বক কোন আনুষ্ঠানিকতায় জড়াতে বাধ্য হন।
[১]
যারা সত্যিই বিশ্বাস করে যে নতুন বছরের নতুন দিন ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ করলে বা ভাল সময় কাটালে সারাটা বছর ভাল কাটবে বা সারা বছর ভাল কাটলেও কাটতে পারে
আমাদের ভাল খারাপ কেবলই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হাতে এবং তিনি না চাইলে কস্মিনকালেও কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল সম্ভব নয়।
“… আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে বলে এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, আপনি বলে দিন, (ভাল-মন্দ) সমস্তকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর এই মানুষগুলোর সমস্যা আক্রান্ত যারা কখনও কোন কথা বুঝতেই চেষ্টা করে না।”
(সূরা নিসা, ৭৮)
ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল ‘তাকদীর’ বা ভাগ্যে বিশ্বাস আর তাকদীরে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ হল ‘যা কিছু হয় তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়, আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনোকিছুই সম্ভব নয়।’
রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “এ পৃথিবীর সমস্ত জাতি যদি একত্রিত হয়ে তোমাদের মঙ্গল করতে চায়, তবে তারা কেবল ততটুকুই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আবার, সমস্ত জাতি যদি একত্রিত হয়ে তোমাদের অমঙ্গল করতে চায় তবে ততটুকুই সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন….।” (তিরমিজী)
তাই যারাই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত অন্যকোনো কার্যকলাপ বা অন্য কোনোকিছুতে মঙ্গল-অমঙ্গল আছে মনে করল বা থাকতেও পারে বলে সন্দেহ পোষণ করল তারাই ‘একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব’ এমন একটি বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করে ফেলল। অর্থাৎ তারা শির্ক করে ফেলল।
তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন –
الطِّيَرَةُ شِرْكٌ
অর্থাৎ, ‘কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শির্ক’।
(আবু দাউদ ৩৯১২; ইবনে-মাজাহ ৩৫৩৮; তিরমিযী, মিশকাত ৪৫৮৪)
রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, “যে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে এবং যাকে সে বিশ্বাস করায়, যে ভাগ্য গণনা করে এবং যাকে সে ভাগ্য গণনা করে দেয়, যে জাদু করে এবং যাকে সে জাদু করে দেয়- তারা আমাদের (উম্মাতে মুহাম্মাদীর) অন্তর্ভুক্ত নয়।”
(সিলসিলা সহীহাহ, ২১৯৫)
তাই ‘মঙ্গল শোভাযাত্রায়’ গেলে সকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়ে মঙ্গল আসবে বা আসতেও পারে এমন ধারণা যে পোষণ করল; অথবা যে নববর্ষের প্রথম দিন ভাল কাটাচ্ছে বলে বাকি বছর ভাল কাটবে বা কাটতেও পারে মনে করল সে নিঃসন্দেহে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। মুসলিমদের অধিকাংশেরই দ্বীনের আকিদাহগত বা মৌলিক বিষয়াদিতেই পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার দরুণ তারা শিরকি আকিদায়, শিরকি কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। ফলে তারা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।
[২]
যারা উপরের এসব বিশ্বাস করে না, কিন্তু এমনিতেই একটু ঘুরে বেড়িয়ে বা স্রেফ একটু ভাল সময় কাটানোর বের হয়
বর্তমানে এই শ্রেণিরই সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তরুণ ছাত্র ছাত্রী ছাড়াও চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এমনকি রিটায়ার্ড মানুষেরাও একটুখানি আনন্দের খোঁজে, পরিবার-আত্নীয়স্বজনদের সাথে একটুখানি ভাল সময় কাটানোর জন্য বৈশাখে ঘুরে বেড়ায়। ব্যস্ত আর নির্লিপ্ত জীবনের একটু অবসাদ খুঁজে ফেরে তারা, খুঁজে ফেরে তারা আনন্দের উপলক্ষ্য।
আপনি হয়তো শোভাযাত্রার, বছরের প্রথম দিন ভাল কাটানোর বা অন্যকোনো বিষয়াদির মঙ্গল অমঙ্গলের ব্যাপারগুলো বিশ্বাস করেন না, বরং আপনি বিশ্বাস করেন ‘সমস্ত মঙ্গল-অমঙ্গল কেবল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে সম্ভব’ কিন্তু তবুও কোনো একটি শির্কযুক্ত কাজ করে মুশরিকদের তালিকায় নাম লিখাতে পারেন। আল্লাহ বলছেন –
“অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে, কিন্তু সাথে সাথে শির্কও করে” (সূরা ইউসুফ, ১০৬)
এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈমানদার মুশরিকদের কথা বলেছেন! তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু সাথে সাথে শির্কের মত জঘন্য গুনাহের কাজেও লিপ্ত হয়!
এই ধরনের শির্ক হল ‘তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ’ অর্থাৎ ‘ইবাদাতে আল্লাহ্র একত্ব অক্ষুন্ন রাখা’ এর বিপরীত। ‘তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ’ এর মাধ্যমে যেমনি ‘ইবাদাতে আল্লাহ্র একত্ব অক্ষুন্ন রাখা’ হয়, তেমনি এর বিপরীতে অন্তরে বিশ্বাস না করলেও মানুষ কোনো একটি কাজের মাধ্যমে শির্কে, কুফরিতে লিপ্ত হতে পারে; আবার কখনো ইসলাম থেকেই খারিজ হয়ে যেতে পারে। তাই অন্তরে বিশ্বাস না করলেও শোভাযাত্রায় যাওয়ার মতো শির্কের কার্যাবলি থেকে নিজেকে হিফাজত রাখাও মু’মিনদের অবশ্যকর্তব্য।
কারণ শির্ক হল কবীরাহ গুনাহের মধ্যেও সবচেয়ে বড় কবীরাহ গুনাহ। এতই মারাত্নক যে, অন্য যেকোনো গুনাহ করা ব্যক্তি তাওবাহ না করলেও আল্লাহ রব্বুল আ’লামীন তাঁর রহমতের অসিলায় ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু শির্ক করে তাওবাহ না করেই মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা কখনো ক্ষমা করবেন না বলে দিয়েছেন।
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যেই আল্লাহর সাথে কোনকিছু শরীক করে সে তো (সরলপথ থেকে) সুদূরে ভ্রান্তিতে পতিত হয়।” (সূরা নিসা, ১১৬)
“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এরূপ অত্যাচারী লোকদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।” (সুরা মায়িদাহ, ৭২)
শুধুমাত্র এই শির্কের ভয়াবহতা নিয়ে শত পৃষ্ঠা লিখা সম্ভব। তার চেয়ে হতভাগা তো কেউ নেই যে কিনা এতকিছু জানলো কিন্তু তবুও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে ঈমানদার হয়েও শির্কে লিপ্ত হল। তার চেয়ে হতভাগা তো কেউ নেই যে কিনা সামান্য একদিন আনন্দ ফূর্তি করার জন্য রব্বের দেওয়া বিধান ভুলে গিয়ে নিজের খেয়াল খুশিকেই, প্রবৃত্তিকেই রবের আসনে বসিয়ে দিল।
“আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকেই স্বীয় উপাস্য করে নিয়েছে?”
(সূরা জাসিয়া, ২৩)
অনেকে হয়তো একটি হাদিসের কথা ভাবেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন “সকল কাজের ফলাফলই নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।” (সহীহ বুখারী, ১) অথচ বেশিরভাগই জানেন না যে, এখানে আসলে ‘ইবাদাত বিষয়ক কাজ’ গুলোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে কাজগুলো ইবাদাত হিসেবেও গণ্য হতে পারে, আবার দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিকও হতে পারে সেগুলো। যেমন কেউ হিজরত করল কিন্তু আল্লাহর জন্য না করে বিয়ে করার জন্য করল এমনসব কাজ এর অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ ভাল নিয়্যাত হলেও কিছু কাজ প্রকৃতিগত কারণেই নিষিদ্ধ আর শির্ক, বিদআতের মত কাজগুলো সেগুলোরই অন্তর্ভূক্ত।
যেমনঃ বিদআতীরা মনে করে যে তারা তাদের নব উদ্ভাবিত ইবাদাত দিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করছে আর আল্লাহকে খুশি করছে অথচ এর মাধ্যমে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুয়্যাতকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। ফলে তাদের মনের নিয়্যাত ভাল হলেও বিদআতী ইবাদাত বাতিল ও গুনাহ আকারে গ্রাহ্য হয়। তাহলে ইবাদাতের নিয়্যাতে করা কাজও গুনাহে পরিণত হতে পারলে আল্লাহর সাথে শির্ক করা হয় এমন কাজের পিছনে ‘নিয়্যাত ঠিকই আছে’ বা ‘বিশ্বাস ঠিকই আছে’ এসব কথা বলে তো মোটেই পার পাওয়া যাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন।
[৩]
যারা মৌলিক আকিদাহ সঠিকই পোষণ করে এবং বৈশাখী কার্যকলাপে সরাসরি অংশ নেয় না। তবে কেবলই বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ঘরে বসে পারিবারিকভাবে বৈশাখ পালন জায়েজ মনে করে বা এভাবে বৈশাখ পালনকে ইসলামবিরোধী কিছু মনে করে না; অথবা এভাবে বৈশাখ পালন অসমর্থন করে না
উৎসবের ছুটির দিনগুলো অন্যান্য সাধারণ ছুটির দিন থেকে হয় আলাদা। কারণ উৎসবের একটা প্রস্তুতি, একটা আয়োজন থাকে। পহেলা বৈশাখ এর ব্যতিক্রম তো নয়ই, বরং প্রস্তুতির দিক দিয়ে আদর্শও বলা যেতে পারে। কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয় জোরশোর প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতিতে থাকে এলাকার মাঠগুলোতে মেলা আয়োজন করে স্টল দেওয়া, রাস্তাগুলোতে আলপনা এঁকে পরে সারাবছর ধরে সেগুলো পাড়িয়ে বেড়ানো আর বটমূলে-হিলে, প্রতিষ্ঠানে-রাস্তায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নাচ-গানের রিহার্সেল। আবার অনেকের থাকে বৈশাখ উপলক্ষ্যে নতুন কাপড় কিনবার, ঘরে স্পেশাল খাবার বানানোর প্রস্তুতি। পত্র-পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র, টিভি আর রেডিও চ্যানেলগুলোর বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা তো বাদই; পান্তা-ইলিশ, কাপড়-চোপড়, মূর্তি মুখোশ থেকে শুরু করে রাস্তার পাশের চটপটি ফুচকা সব ধরনের ব্যবসার এমন রমরমা উপলক্ষ্য তো খুব কমই আসে। সব মিলিয়ে বাঙালিয়ানা যেন ধর্ম, আর বৈশাখ যেন সেই ধর্মের ঈদ।
আমার মতো কোনো আব্দুল্লাহ বলে ফেললেই মেনে নিবেন, তা নয়। বরং কুরআন আর সুন্নাহই আপনার দলিল হোক। বাঙালি পরিচয় বড় নাকি মুসলিম পরিচয় বড় আগে সেটা নির্ধারণ করুন।
উত্তরটা বাঙালি হলে আপনি এখনও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারই হতে পারেন নাই। শুধু তাই নয়, আপনি ‘আস-সাবিয়্যাহ’ তে আক্রান্ত এবং জাহিলিয়াতে রয়ে গেছেন। আর ‘আস-সাবিয়্যাহ’ তে আক্রান্তদের মত বোকা আর অথর্ব খুব কম মানুষই হতে পারে। কারণ জন্মভিত্তিক পরিচয়গুলো স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তির বাহিরে। কেউ ধনীর ঘরে জন্মাবে নাকি গরীবের ঘরে সেটা নিজে যেমনি নির্ধারণ করতে পারে না, তেমনি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মাবে নাকি ইংরেজদের ঘরে জন্মাবে সেটাও তার ক্ষমতার বাহিরে। তাই বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ভাষা নির্বিশেষে যেকোনও মানুষই আল্লাহর কাছে প্রিয় বা ঘৃণ্য হতে পারে সে বিষয়টির মাধ্যমে যেটা বেছে নেওয়ার ও মেনে চলার পছন্দ মানুষকে দেওয়া হয়েছে – আল্লাহর নিকট আত্নসমর্পণ তথা মুসলিম হওয়া ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করা।
তাহলে কেউ কেউ মুসলিমের ঘরে আর কেউ কেউ অমুসলিমের ঘরে জন্ম নিচ্ছে সেটা? আল্লাহ কারও উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। কেউ অমুসলিম ঘরে জন্মালে সেটাই তার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষা। আর সে শেষ বয়সেও মুসলিম হলে যে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে সেটাও তো এক ঈর্ষণীয় পাওয়া। আর অবশ্যই আল্লাহ কারও প্রতি জুলুম করবেন না।
আর আপনার কোন পরিচয়টা বড় সেই প্রশ্নের উত্তরটা ‘মুসলিম’ হলে আপনার জন্য কুরআন সুন্নাহের দালিলিক আলোচনাই যথেষ্ট হবে।
রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক জাতির নিজস্ব উৎসব রয়েছে, আর আমাদের জন্য সেটা ঈদ।” (সহীহ বুখারী: ৯৫২; সহীহ মুসলিম: ৮৯২)
অর্থাৎ বাঙালি জাতির উৎসব পহেলা বৈশাখ থাকলেও একজন মুসলিমের জন্য তা নয়। মুসলিমের জন্য উৎসব হল দুই ঈদ।
আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে এই তথাকথিত বাঙালি সংস্কৃতি আসলে সনাতন ধর্মালম্বীদের বিভিন্ন শির্কযুক্ত কুসংস্কার আর মূর্তিপূজার সংস্কৃতি। আর ইসলামী জীবনব্যবস্থার রয়েছে সম্পূর্ণ নিজস্ব আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি: মুসলিমদের জন্য ভিন্ন কোন সম্প্রদায় যেমন: মুশরিক কিংবা অগ্নিপুজারীদের সংস্কৃতি, ইহুদী, নাসারা, বা আচার-আচরণ অনুকরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
রাসুল ﷺ বলেছেন: “কেউ যদি কোন সম্প্রদায়কে অনুকরণ করে, তবে তাকে (শেষবিচারের দিনে) তাদের একজন বলে গণ্য করা হবে।” ( আবূ দাঊদ, ৪০৩১)
একারণে ঘরে বসে পারিবারিকভাবেও বাঙালি সংস্কৃতির নামে বৈশাখ পালন করা যাবে না, যাবে না এর সমর্থন করাও।
হযরত আনাস (রদিআল্লাহু আ’নহু) থেকে বর্ণিত আছে যে যখন আল্লাহর রাসূল মদিনায় আসলেন, তখন মদিনার অধিবাসীদের দুটো উৎসবের দিন ছিল, যে দিনগুলোতে তারা আনন্দ-উৎসব করতো।
তিনি ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, “এ দিনগুলো কীসের জন্য?”
তারা বলল, “জাহেলিয়াতের যুগে আমরা এ দিনগুলোতে আনন্দ উৎসব করতাম।”
তখন আল্লাহ’র রাসুল (সা) বললেন, “আল্লাহতায়ালা তাদের এই দুটো দিনের চাইতে উত্তম দুটো দিন তোমাদের দান করেছেন। আর তা হল: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা’র দিন।”
(আবু দাউদ, ১১৩৪)
উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এত সুস্পষ্ট নির্দেশনা আসার পরও ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ কথাটিকে রীতিমত কালাম বানিয়ে বৈশাখ পালন করা সহজ, কঠিন হল মুসলিম হিসেবে কেবল আল্লাহর ইচ্ছাকেই সর্ববিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া। কারণ, মুসলিম শব্দের অর্থই তো ‘যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে’।
এছাড়া ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ কথাটিকে তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও ‘ইসলাম’ অন্যসব ধর্ম থেকে আলাদা। কারণ ইসলাম কেবলই ধর্মবিশ্বাসে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলাম হল একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ‘দ্বীন’ তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।
“বিধান হচ্ছে আল্লাহর এবং তিনি বিধান দিয়ে দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদাত করো না।” (সূরা ইউসুফ, ৪০)
আর এই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানে উৎসবের ব্যাপারেও যে সুনির্দিষ্ট আদেশ নিষেধ দেওয়া হয়েছে তা তো উপরের আলোচনাতেই প্রতীয়মান। এরপরও যদি নিজ খেয়াল খুশিকে রবের আসনে বসাতে চান তাহলে আপনার ব্যাপার।
“এবং যে কেউই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনব্যবস্থা আকাঙ্খা করবে, তা কখনোই তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না, এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন৷” (সূরা আলে ইমরান, ৮৫)
[৪]
যারা সত্যিই কোনো প্রয়োজনীয় কাজে বৈশাখের দিন বের হয় ।
প্রথমেই প্রয়োজনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যাক। প্রয়োজনের সংজ্ঞার দুটো দিক বিবেচনা করা উচিত আর সেগুলো হল – এক, এমন অত্যাবশ্যকীয় পরয়োজন যা আপনার পহেলা বৈশাখের দিনেই করতে হবে। দুই, আপনি এই প্রয়োজন সম্পর্কে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবেন।
পহেলা বৈশাখের কুসংস্কার বা শিরকি কার্যকলাপ সম্বন্ধে বান্দা ওয়াকিবহাল। তাই সে শোভাযাত্রা, মূর্তিযাত্রা হেন তেন ইত্যাদিতে গেল না। কিন্তু বিকাল বা সন্ধ্যার দিকে মেলায় কিছু একটা কিনবার অসিলায় বা এমনিতেই ঘুরতে বের হল। বোঝা উচিত, এগুলো প্রয়োজনের সংজ্ঞাতেই পড়বে না। বাদবাকি যারা মনে করেন যে আপনারা আল্লাহর সামনে নিজের এই কাজ নিয়ে দাঁড়াতে পারবেন তাদের জন্য এই অংশ।
পহেলা বৈশাখ আর অন্যান্য জাহিল উৎসবে যে পরিমাণ অবাধ মেলামেশা আর বেপর্দা বেহাপনার সৃষ্টি হয় শুধু এই কারণেই মুসলিম হিসেবে এই পহেলা বৈশাখ সম্পূর্ণ বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। এই ধরনের জাহিলিয়াপনায় যে শুধু চোখের জিনাই সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলে তা বিবেকবান প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারে।
“…চোখের জিনা হল (অশ্লীল উদ্দেশ্যে) তাকানো, জিহ্বার জিনা হল (অশ্লীল) কিছু বলা…” (বুখারি ৫৮৮৯, মুসলিম ২৬৫৭)
কিন্তু এই বেহায়াপনা যে শুধু চোখে আর মুখেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই তার প্রমাণও পেয়ে গেছে মানুষ। কিন্তু তারও আগে আরও কত বোনকে যে ভিড়ের মধ্যে সুযোগের বলি হতে হয়েছে তা তো কেবল আল্লাহই জানেন। এখানে উল্লেখ্য যারাই এমন দিনে বের হয়ে নিজেদেরকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে, আর নিজেরা সেজে গুজে ফিতনাহ হয়ে বের হচ্ছে উভয়ই অপরাধী। ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কম বা বেশি হতে পারে, কিন্তু এদের কেউই নিরপরাধ নয়। আল্লাহ ক্ষমা করুন।
“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে তা সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত আছেন।” (সূরা নূর, ৩০)
“ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে … … … তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (সূরা নূর, ৩১)
আল্লাহ রব্বুল আ’লামীন মুমিন-মুমিনা উভয়ের জন্য আলাদা আয়াত নাযিল করে পর্দা ফরজ করেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গেলেও বই হয়ে যায়। যেসব বোনেরা মনে করেন যে হিজাব করেও বাহিরে বের হওয়া যায় তারা আসলে হিজাবকে বুঝতেই পারেন নাই। এই বিষয়ে
‘ইসলামে নিকাব নেই’ নোটে কিছুটা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।
ফিতনার এই ব্যাপারটি জাহিলরাও অস্বীকার করে না, অথচ অনেক মুসলিমকেই কেবল একদিনের সস্তা আনন্দের লোভে রবের ভয় ভুলে যায়। ‘বখাটে ছেলেদের ভীড়ে ললনাদের রেহাই নাই’ যখন গানের লিরিকসে চলে এসেছিল তা জেনেবুঝেই এসেছিল। আমাদের এখন নিজেদের দোষত্রুটিগুলো মেনে নিয়ে আল্লাহকে যথার্থ ভয় পাওয়া উচিত।
উল্লেখ্য, যে পুরুষ পরিবারের দায়িত্বে নিয়োজিত, তিনি যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়েন, তাহাজ্জুদ পড়েন, নফল ইবাদাতে মশগুল থাকেন, মুখে দাঁড়ি রেখে ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে চলাফেরা করেন, সমাজে ভদ্রজন হিসাবে পরিচিতিও পান, কিন্তু তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে বেহায়াপনায় বাধা প্রদান করেন না, উত্তমভাবে নজরদারি করেন না, এমন ‘ভদ্রজন’দেরকেও হাদীসে ‘দাইয়ূস’ বলা হয়েছে।
দাইয়ূস হলো সে ব্যক্তি যে তার পরিবারকে বেহায়াপনার সুযোগ দেয়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপরে জান্নাত হারাম করেছেন; মদ্যপায়ী, পিতামাতার অবাধ্য ও দাইয়ূস। যে তার পরিবারে অশ্লীলতাকে স্বীকৃতি দেয়’ (দাইয়ূস)।”
(সহীহুল জামি’ ৩০৫২)
তাই অভিভাবক মহল, আপনাদের নিজেদের সন্তানদেরকে গুনাহে জারিয়ার উপলক্ষ্য বানাবেন না। সচেতনতার অভাবে যদি আপনার সন্তান নষ্ট হয় তবে আপনি আল্লাহর নিকট কী জবাব দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ৩৬৮৫)
তাই যেসব প্রয়োজন নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো যাবে না, সেগুলো অনুধাবণ করুন আর তা থেকে দূরে থাকুন। সলাত, অসুস্থতা যার কারণে ডাক্তারের কাছে যাওয়া অয়াবশ্যক হয়ে পড়ে এই ধরনের প্রয়োজন ছাড়া যেসব প্রয়োজনীয় কাজ একদিন পরেও করা সম্ভব সেগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির রাহে পরেই করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
[৫]
যারা প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবরদস্তিপূর্বক কোন আনুষ্ঠানিকতায় জড়াতে বাধ্য হন ।
এই বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষাস্বরূপ এবং এক্ষেত্রে পরিস্থিতিভেদে শিথিলতা আসতে পারে। বিষয়টি আলেমদের সাথে পরমার্শ করাই বাঞ্চনীয়। তবে এখানেও অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ভয়ের দাবিদার।
একেবারে বাধ্য হলেও আল্লাহর কাছে বিষয়টির জন্য ইস্তিগফার করতে হবে এবং তাওবাহের সমস্ত শর্তগুলো পূরণ করে আন্তরিকভাবে তাওবাহ করতে হবে। ভাগ্যের পরিহাসে লিখাটি যাদের ‘পহেলা বৈশাখ’ পালন শেষে পড়া হবে তাদের জন্যও তাওবাহ বাঞ্চনীয়। তানাহলে চৈত্র্যের শেষে বৈশাখের উত্তাপ কোনোরকম সহ্য করতে পারলেও জাহান্নামের উত্তাপ কিন্তু সহ্য হবে না মোটেও।
“…নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়।…” (সূরা বাকারাহ, ১৯৭)
“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” ( সূরা আল-ইমরান, ১০২)
“কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ।…” ( সূরা আল-ইমরান, ১৯৭)
ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।
আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝার, দ্বীনে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করার তাওফিক দিন এবং সিরতল মুস্তাকিমে অটল অবিচল থাকার তাওফিক দিন। আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম তওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ’লামীন, ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আ’লা রসূলিহী ওয়া আস-হাবিহি ওয়াসাল্লাম তাসলিমান কাসি-র।
====================
লেখক- তানভীর আহমেদ