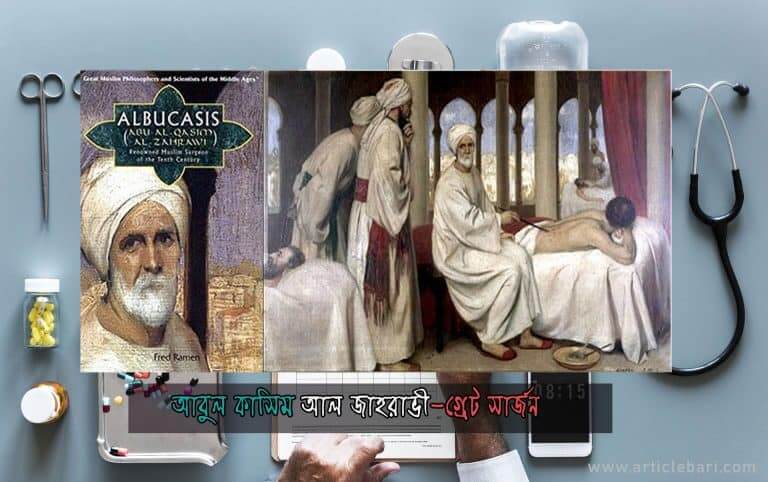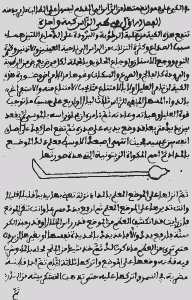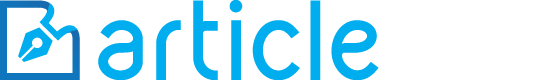নারী ও পুরুষের সমন্বিত প্রয়াস ও অংশীদারিত্বে মানব জাতির বিকাশ হয়েছে। সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণে নারী বা পুরুষ কারো ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবতা হচ্ছে, মানব জাতি যখন যেখানে আসমানী শিক্ষা হতে দূরে সরে গেছে, সেখানে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং অশান্তির আগুন মানব জীবনকে ঘিরে ফেলেছে। বিশেষ করে পৃথিবীর শুরু হতে নারী পুরুষ একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও উভয়ের মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। এতে সবচে বেশি শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে সৃষ্টিগতভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও লোভনীয়-মাহনীয় রূপের আধার নারী সমাজ। নারী তখন পুরুষের ফুর্তি ও ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। বলা হয়েছে সমাজের চরম নিগৃহ ও বঞ্চনা নারীর ভাগ্যফল আর পুরুষ হল স্বামী ও পতি।
ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবে ও ভারতের নারী সমাজ
প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেন তখনকার আরব সমাজে নারীরা কতভাবে বঞ্চনার শিকার ছিল, তার চিত্র ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। এর সামান্য একটি নমুনা ছিল, মেয়ে শিশুর জন্মকে গোটা পরিবারের জন্য কলঙ্কজনক মনে করা হত। তাই জন্মের সাথে সাথে তাদেরকে জীবন্ত কবরে পুতে ফেলা হত। ঠিক একই সময়ে ভারতীয় সমাজে চলছিল অন্যরকম চিত্র ও নিগ্রহ। ভারতীয় সভ্যতায় নারীকে মনে করা হত স্বামীর ভোগের সামগ্রী। তাই স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে স্বামীর লাশের সাথে চিতায় গিয়ে আগুনে পুড়ে প্রাণ দিতে হত। এমন পরিস্থিতিতেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধূলির ধরায় আবির্ভূত হন। তার প্রচারিত ইসলামের ছায়াতলে নারী তার অধিকার ও সম্মান ফিরে পায়। এ কারণে দেখা যায় নারী তার মানবিক সত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় কালজয়ী ভূমিকা পালন করেন।
প্রথম যেভাবে ওহী নাযিল হল:
মক্কার ছয় কিলোমিটার উত্তর পূর্বে জাবলে নূর, নূর নামক পবর্ত। এই পর্বতের উপরে একটি গুহায় কয়েক বছর থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাসের জন্য চলে যেতেন আল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন আরাধনা ও ধ্যানমগ্নতায় কাটানোর জন্য। একদিন রাতে তিনি ঘুমিয়েছিলেন। কেউ এসে তাকে ঘুম থেকে জাগালেন আর সবুজ মখমল কাপড়ে জড়ানো একটি ফলক মেলে ধরে বলেন, পড়–ন। নবীজি বললেন, আমি পড়তে পারি না। ফেরেশতা তাকে বুকে আলিঙ্গন করে প্রচ- চাপ দেন। তাতে তিনি প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করেন। ফেরেশতা আবারো বলেন, পড়–ন। তিনি আবারো জবাব দেন, আমি পড়তে পারি না। ফেরেশতা আবারো তাকে বুকে আলিঙ্গন করে প্রচ- চাপ দেন, এবারও তিনি প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করেন। ফেরেশতা বললেন, ‘পড়–ন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শুক্রবিন্দু হতে। পড়–ন, আপনার প্রভু অতিশয় দয়ালু, যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত আগন্তুক ফেরেশতা পাঠ করার সাথে সাথে হযরতের অন্তরে অঙ্কপাত করল। তিনিও আয়াতগুলো আবৃত্তি করলেন। ফেরেশতা নিজের পরিচয় দিলেন ফেরেশতা জিব্রাঈল বলে। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় নবীজি আতঙ্কিত হলেন। তিনি কম্পিত দেহে বাড়ি ফিরে ঘরের লোকদের ডেকে বলেন, যাম্মিলুনী, যাম্মিলুনী। তোমরা আমাকে চাদর ঢেকে দাও। আমাকে চাদর জাড়িয়ে দাও। আমি আমার জীবন নিয়ে শংকিত।
বিবি খদিজা রা. নবীজির অনুপম চরিত্রের সাক্ষী
স্ত্রী খদিজা স্বামীর মুখে ঘটনার বর্ণনা শুনে ভয়ে আতঙ্কে আরো ঘাবড়ে যাওয়ার কথা। জিব্রাঈল নামে কারো কথা তো তিনি এর আগে শুনেন নি। না জানি, কোনো বিপজ্জনক দৈব কিছু ঘটল কিনা। বুদ্ধিমতি বিচক্ষণ খদিজা চিন্তা করলেন, আজীবন তার স্বামী সত্য ও সুন্দরকে লালন করেছেন। কাজেই তার জীবন কখনো বিপত্তির মুখে পড়তে পারে না। তবে প্রথম কাজ হবে স্বামীর মন থেকে অজানা আতঙ্ক দূর করা। কাজেই চাদর মুড়ি দিয়ে তাকে বিশ্রাম নিতে দিলেন। এরপর প্রচ- আত্মবিশ^াস নিয়ে অভয় দিলেন, (সীরাতে ইবনে হিশামের বর্ণনায় ) ‘আপনি আনন্দিত হোন। সুসংবাদ আপনার জন্য। আমি তো আশা করি, আপনি হবেন এই জগতের জন্য আল্লাহর বার্তা বাহক প্রেরিত পুরুষ। আপনি হবেন শেষ জমানার নবী। ’ তিনি তার এই আশাবাদের পেছনে যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করলেন তাও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তার মধ্যে নবী জীবনের এক সুন্দর আলোকিত দিক ফুটে উঠেছে। বুখারী শরীফের বর্ণনায় হযরত খদিজা নবীজির উদ্দেশ্যে বললেন, ‘কক্ষণো না, ভয়ের কিছু নেই। আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। দুর্বল ও দুস্থ লোকদের সেবা করেন। বঞ্চিত ও অভাবীদের উপার্জনক্ষম করেন। মেহমানদের আতিথেয়তা করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদগ্রস্থদের সাহায্য করেন।’
ভালো মানুষ কিনা দেখার আয়না নিজের স্ত্রী:
হযরত খদিজাতুল কুবরার এই সাক্ষ্য প্রমাণ করে নবুয়াত লাভের আগে থেকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মানব সেবা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। দ্বিতীয়ত তিনি কত মহান মানুষ ছিলেন তার সবচে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত নিজের স্ত্রীর সাক্ষ্য। মানুষ বাইরের সমাজে বিরাট কিছু হতে পারে। কিন্তু ভেতরে আসল মানুষটি কেমন তা অবশ্যই ধরা পড়ে স্ত্রীর আয়নায়। স্ত্রীর কাছে কোনো কিছু গোপন থাকে না, রাখতে পারে না। এ জন্যে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম।’ নিঃসন্দেহে নবুয়াত লাভের পূর্বে খদিজা রা. নবীজির চরিত্র এবং ভবিষ্যতে মানব জাতির পথপ্রদর্শক হওয়ার যে ভবিষ্যতবাণী করলেন, তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মানুষ যখন কোনো নতুন কাজের উদ্যোগ নেয়, তখন স্ত্রী তথা পরিবার থেকে সামান্য সমর্থন কাজটি এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কীরূপ ভূমিকা রাখে তার অভিজ্ঞতা কম বেশি আমাদের সবার আছে। নবী করিম সা. এর নবুয়াতী জীবনে খাদিজাতুল কুবরার অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য গোটা উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত তার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জগতের সর্বপ্রথম মুসলমান ছিলেন একজন নারী আর তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মীনী আমাদের মা হযরত খাদিজাতুল কুবরা রা.। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন চল্লিশ বছর ও একদিন তখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়। ওহী নাযিলের অত্যন্ত কঠিন ও স্পর্শকাতর মুহূর্তে হযরত খাদিজা যে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়ায় অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন তা ইতিহাসের বিস্ময়।
বিবি খাদিজা রা. যেভাবে পরিস্থিতি সামাল দিলেন
দূরদর্শী খাদিজার নবীজিকে মৌখিক সান্ত¡না দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। তিনি জানতে চান, জিব্রাঈল নামে যিনি তার স্বামীর কাছে আসল তার পরিচয় কী? পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য তিনি চলে গেলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে। ওয়ারাকা ছিলেন খ্রিস্টান পাদ্রী। ইঞ্জিল লিখতেন এবং ধর্মগুরু হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। খাদিজা রা. তার কাছে একা গিয়েছিলেন বা নবীজিকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। বুখারী শরীফের বর্ণনায় ‘খাদিজা নবীজিকে সঙ্গে নিয়ে তার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল ওযযার কাছে গেলেন। ওয়ারাকা জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ও তওফীক অনুযায়ী তিনি ইঞ্জিলের অনেকাংশ (সুরয়ানী ভাষা থেকে) হিব্রু ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা তাকে বললেন, হে চাচাত ভাই। আপনার ভাতিজা (অর্থাৎ নবীজি) এর কাছ থেকে সবকথা শুনুন।
ঘটনার বিবরণ শুনে ওয়ারাকা তাকে বললেন, এই সেই নামুস, (পবিত্র ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসা এর নিকট নাযিল করেন। হায়! আমি যদি তোমার নবুয়তের সময় বলবান যুবক থাকতাম। হায়! যদি আমি সেই সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ারাকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ তুমি যা নিয়ে দুনিয়ায় এসেছ তদ্রুপ কোনো কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। তারপর ওয়ারাকা বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। এরপরই ওহী নাযিলে বিরতি ঘটে।
আগন্তুক ফেরেশতা না শয়তান জানার অভিনব পরীক্ষা
ওহী নাযিলের প্রথম দিকে নবীজিকে মনোবল যোগানো, আগত ফেরেশতার প্রকৃত পরিচয় জানা এবং পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য খাদিজাতুল কুবরা রা. আরো পদক্ষেপ নেন। সীরাতের কিতাবসমূহে তার বিস্তারিত বিবরণ বিধৃত। সীরাতে ইবনে হিশামে একটি রেওয়াত বিধৃত হয়েছে ইসমাঈল ইবনে আবি হাকাম সূত্রে। তাতে খদিজা রা. নবীজিকে বলেন, আপনার কাছে যখন আপনার সাথী আসে তখন কি আমাকে জানাতে পারেন? বললেন, হ্যাঁ, জানাব। একদিন যখন জিব্রাঈল এলেন নবীজি খদিজাকে ডেকে বললেন, খদিজা আমার সাথী এখন এসেছে। খদিজা রা. বললেন, হে আমার চাচাত ভাই! কাউকে সম্বোধন করতে চাচাত ভাই বলা তখনকার আরব সমাজে একটি রেওয়াজ ছিল। খাদিজা বললেন, আপনি উঠে আমার বাম হাঁটুর উপর বসুন তো। নবীজি দাঁড়িয়ে তার হাঁটুর উপর বসলেন। খাদিজা বললেন, আপনি কি তাকে এখন দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর বললেন, এবার পাল্টে এসে আমার ডান হাঁটুর উপর বসুন। হযরত সরে এসে খাদিজা রা. এর ডান হাঁটুর উপর বসলেন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন? বললেন, হ্যাঁ। বললেন, এবার উঠে আমার পাশে বসুন। নবীজি সরে এসে তার পাশে বসলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি দেখতে পাচ্ছেন? বললেন, হ্যাঁ। এ সময় খাদিজা রা. মাথার ওড়না খুলে ফেললেন। তখনও নবীজি তার পাশেই বসা ছিলেন। এবার জানতে চাইলেন আপনার আগন্তুক সঙ্গীকে কি দেখতে পাচ্ছেন? নবীজি বললেন, না দেখছি না। তখন খদিজা রা. আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, হে চাচাত ভাই! আপনি আনন্দিত হোন। আপনি অবিচল থাকুন। আপনার জন্য সুসংবাদ। আপনি যাকে দেখতে পান তিনি ফেরেশতা। শয়তান (দুষ্টজিন) নয়। (কারণ ফেরেশতা বেপর্দা মহিলার কাছে থাকে না। আগন্তুক শয়তান বা জিন হলে মাথার কাপড় ফেলে দিলে চলে যেত না। )
হযরত খদিজাতুল কুবরার অবর্ণনীয় ত্যাগ
হযরত খদিজাতুল কুবরা রা. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতী মিশনের জন্য যে ত্যাগ, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি বিশে^র বুকে আল্লাহ আল্লাহর রসূল ও তাঁর আনীত বাণীর প্রতি প্রথম বিশ^াস স্থাপনকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। বিশে^র বুকে প্রথম মুসলমান একজন মহিলা এটি কি মুসলিম নারীদের জন্য কম গৌরবের বিষয়? ওহী নাযিলের আগেও হেরাগুহায় নবীজি যখন ধ্যানমগ্ন থাকতেন তখন তাঁর খাবার ও পানীয় সরবরাহ করতেন হযরত খদিজা রা.। সাধারণত মহিলারা স্বামীর আয় উপার্জনের দিকেই দৃষ্টি রাখে। অথচ স্বামীর প্রতি খদিজাতুল কুবরার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যরকম। খদিজা ছিলেন আরবের ধনাঢ্য মহিলা। তার পুঁজি নিয়েই বিবাহের আগে নবীজি সিরিয়ায় বাণিজ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর নিজের সমস্ত সম্পদ তিনি উৎসর্গ করেন নবীজির কদমে। তাঁর গোটা জীবন, জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন ইসলামের সেবায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যে। ইসলামের জন্য হযরত খদিজার আত্মত্যাগ কতখানি তা বুঝার জন্য একটি হাদীসের মর্মবাণী সামনে রাখাই যথেষ্ট।
হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই খদিজার কথা স্মরণ করতেন তাঁর প্রশংসা করতেন। এবং এই প্রশংসা হত অনেক দীর্ঘ ও সুন্দর। একদিন খদিজার অতিবেশি প্রশংসা শুনে আমার আত্মমর্যাদায় লাগল। আমি নবীজিকে বলে ফেললাম, আপনি একজন বুড়ির প্রশংসায় এভাবে আত্মহারা হয়ে যান। সে তো মরে গেছে আর আল্লাহ আপনাকে তার চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। একথা শুনে নবীজি বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ আমাকে খাদিজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেন নি। (খাদিজার চেয়ে উত্তম কেউ হতে পারে না। কেননা, ) মানুষ যখন আমাকে অস্বীকার করেছিল তখন সে আমার উপর ঈমান এনেছিল। লোকেরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল খাদিজা তখন আমাকে সত্য বলে বিশ^াস করেছিল। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চনার শিকার করেছিল তখন আল্লাহর তার সম্পদ দিয়ে আমাকে অভাবমুক্ত করেছিল। আর আল্লাহর তার ঘরে আমার সন্তানদের দিয়েছেন (ইবরাহীম ছাড়া বাকী সবাই খদিজার ঘরের সন্তান)
খাদিজার ইন্তেকালে নবীজির দুঃখ ও শোক:
বুখারীসহ সব হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে এই হাদীসের বর্ণনা এসেছে। বস্তুত হযরত খাদিজা ছিলেন নবীজির পারিবারিক শান্তি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও শান্তির ঠিকানা। এ কারণে নবুওয়াতের ১০ম সালে যখন চাচা আবু তালেবের ইন্তিকালের পরপর বিবি খাদিজাও ইন্তিকাল করেন তখন নবীজি সামাজিকভাবে চরম অসহায়ত্বের শিকার হয়েছিলেন। তিনি সেই বছরটিকে আম্মুল হাযান বা দুঃখের বছর হিসেবে জীবনভর স্মরণ করেছেন। নবীজির পাশে থেকে খাদিজাতুল কুবরার ত্যাগ ও কুরবানী প্রমাণ করে, শুরু থেকে মহিলারা ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় শুধু যে অবদান রেখেছিলেন তা নয়; বরং এ ক্ষেত্রে তারা পুরুষের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।
মহানবী সা. এর বহুবিবাহের রহস্য
এখানে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে সামনে এগুতে চাই। নবীজির সংসারে আমাদের মায়েদের সংখ্যা ছিল বরাবর ৯ জন। খাদিজা রা. ও আরো কয়েকজনকে হিসাবে আনলে এই সংখ্যা ১১ বা ১৩। পশ্চিমা দুনিয়ার বিদ্বেষী অন্ধদিল নিন্দুকদের গাত্রদাহ হল, ইসলামের নবীর সংসারে স্ত্রীর সংখ্যা এতবেশি কেন? তারা একে ‘নাউজু বিল্লাহ’ নবীজি নারীলোভী ছিলেন বলে অপপ্রচার চালাতে সুখ অনুভব করে।
আমাদের আলোচনা ইসলামে নারীর অবদান নিয়ে। তাই এই প্রশ্নে এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না। খুব সংক্ষেপে বলতে চাই, একজন পুরুষের যৌবনের তাড়না বা কামনা থাকে ১৫ বছরের পর থেকে চল্লিশ বছর বা বড়জোর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত। কেউ নারীলোভী হলে এ সময়েই তার চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে। অথচ আমরা দেখি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন ২৫ বছর তখন কুরাইশ বংশের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বিদুষী মহিলা খাদিজা, যার বয়স চল্লিশের কোটায় এবং ইতিমধ্যে দুজন স্বামীর সাথে ঘর করেছেন, সন্তান আছে তার সাথেই পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। নবুয়াত লাভের পরের কঠিন দিনগুলোতে সে স্ত্রীই তার আশ্রয়স্থলের ভূমিকা পালন করেন।
পঞ্চাশ বছর বয়সে দ্বিতীয় বিবাহ
নবুয়াতের দশ সাল অর্থাৎ নবীজির বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে স্ত্রী খাদিজা মারা গেলে তিনি শোক ও দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হন, যে কারণে বছরটিকে তিনি দুঃখের বছর হিসেবে অভিহিত করেন। খাদিজা রা. এর ইন্তিকালের পর যে মহিলার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তিনি ছিলেন আবিসিনিয়া হিজরতকারী ও পরে মৃত সাহাবী সুকরানের বিধবা স্ত্রী সাদিয়া বিনতে যামআ রা.।
নবুয়তের ১৩ বছরে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের ২ বছর আগে অর্থাৎ ৫১ বছর বয়সে যাকে বিবাহ করেন তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ছয় বছর বয়েসী কন্যা হযরত আয়েশা রা.। বিয়ে হলেও স্ত্রী হিসেবে তাকে ঘরে তোলেন তিন বছর পরে, তখন আয়েশা রা. এর বয়স হয়েছিল ৯ বছর।
চার বছরের ব্যবধানে আটজন স্ত্রী গ্রহণ:
হিজরতের ৩ থেকে ৭ বছরে নবীজি আরবের বিভিন্ন গোত্রের বিদুষী রমনী, যুদ্ধে শহীদ বা এমনিতে মারা যাওয়া সাহাবীর বিধবা স্ত্রীকে। এই সংখ্যা ছিল ৮জন। এসব বিবাহের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ এড়ানো, গোত্রীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও অসহায় নারীকে আশ্রয় দান। ইতিহাস বলে ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর যখন পরিস্থিতি ইসলামের অনুকুলে এসে যায় তখন থেকে ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত নবীজি আর কোনো নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নি। কাজেই যে মহাপুরুষ যৌবনের শুরু থেকে ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত একজন মাত্র স্ত্রীকে নিয়ে ঘর সংসার করলেন, পরে যাদের বিয়ে করলেন, একজন বাদে তাদের সবাই ছিল বিধবা এবং জীবনের শেষ তিন বছর আর কোনো নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন না, যারা তার চরিত্র হনন করার দুঃসাহস দেখায় তারা আল্লাহর দুনিয়ায় সবচে বড় পাপিষ্ঠ।
ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী নবীজির বহুবিবাহের মূল কারণ ছিল মানব জাতির অর্ধেক নারী সমাজে ইসলামের বিস্তার ও ইসলামী জীবন প্রণালী শিক্ষা দান। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন গোটা মানব জাতির জন্য। কিন্তু মানব জাতির অর্ধেক তো নারী সমাজ। কিন্তু নিজে পুরুষ হওয়ার কারণে নারীদের একান্ত বিষয়াদি সরাসরি শিক্ষা দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল, ফলে তার সতীসাধ্বী বিবিগণের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেক মায়ের নিজস্ব গৌরবময় ভূমিকা ছিল। তবে যাদের অবদান ইসলামের ইতিহাসকে অধিক আলোকিত করেছে তারা হলেন হযরত আয়েশা রা. ও হযরত উম্মে সালামা রা.।
হযরত আয়েশা রা. এর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব:
আমাদের মা হযরত আয়েশা রা. কে নবীজি আদর করে ডাকতেন হুমায়রা। তবে আসল নাম আয়েশা। সিদ্দিকা ছিল তার উপাধি। এই উপাধি পিতা আবু বকর আতীক ইবনে আবি কুহাফা সূত্রে প্রাপ্ত। তার উপাধি ছিল সিদ্দিক (পরম সত্যবাদী)। তিনি ইসলামের প্রথম খালিফা ও পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর সর্বাধিক সম্মানের পাত্র। হযরত আয়েশা রা. এর বয়স যখন ৬ বছর, তখন হিজরতের দুই বছর পূর্বে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তাকে বিয়ে দেন আবু বকর সিদ্দিক রা.। দ্বিতীয় হিজরীতে তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংসারে গমন করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। তিনি ছিলেন অন্যান্য বিবিগণের মাঝে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সর্বাদিক প্রিয়। এ কারণে পালাক্রমে যেদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে থাকতেন, সেদিন সাহাবায়ে কেরাম হযরতের কাছে হাদিয়া উপহার বেশি পাঠাতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার ঘরে ও তাঁর কোলে ওফাত লাভ করেন। সেই ঘরেই তিনি সমাহিত হন। সে ঘরই এখন রওযা আকদাস হিসেবে দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে সবচে প্রিয় স্থান।
হযরত আয়েশা রা. ছিলেন নবীজির প্রাণের সান্তনা:
হযরত আয়েশা রা. সূত্রে হাদীসের জ্ঞান ছাড়াও মহিলা সংক্রান্ত শরীয়তের অনেক বিধান লাভ করে মুসলিম উম্মাহ। তবে সবচে বড় অবদান ছিল তিনি ছিলেন নবীজির মনের সান্ত¦না। কোনো ব্যস্ততা বা আধ্যাত্মিক ভাবের তন্ময়তায় যখন নবীজির মন ভারি হয়ে যেত তখন মনের সান্ত¡নার খুঁজে হযরত আয়েশাকে ডেকে বলতেন: কাল্লিমীনী ইয়া হুমাইরা। ‘হে হুমায়রা তুমি আমার সাথে কথা বল, আমার মন হলকা কর।’ নবুয়তের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একজন মহিলার এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? বর্ণিত আছে, নবীজি যখন একই বিছানায় একই চাদরের নিচে হযরত আয়েশার ঘরে বিশ্রাম নিতেন তখনও তার উপর ওহী নাযিল হত।
হযরত আয়েশা রা. এর ব্যক্তিত্ব ও অবদান:
হযরত আয়েশা রা. এর প্রচুর কবিতা মুখস্থ ছিল। অর্থাৎ সাহিত্য চর্চায় তিনি অগ্রণি ছিলেন। এছাড়া তিনি রোগীদের চিকিৎসা করতেন। মানুষ চিনতে তার মেধা ও প্রজ্ঞা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ইসলামের প্রথম শ্রেণীর আলেম ও ফকীহ ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে যে ৭ জন ফিকাহশাস্ত্রে শিরোমণি ছিলেন, হযরত আয়েশা রা. তাদের অন্যতম। সেই ৭ জন ছিলেন হযরত উমর রা., হযরত আলী রা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ রা., হযরত আয়েশা রা. হযরত যায়দ ইবনে সাবেত রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.। বাকী ১৩৩ বা ১৩৯ জন ফকীহ সাহাবীর অবস্থান এই ৭ জনের পরে। হযরত আয়েশা রা. হতে ২ হাজার ২শ ১০ টি হাদীস বর্ণিত। হযরতের জীবদ্দশায় ও ওফাতের পরে নানা ঘটনা প্রবাহে হযরত আয়েশা রা. মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। হযরত ওসমান রা. এর খেলাফতের শেষদিকে উটের যুদ্ধে তিনি অগ্রণি ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ নিয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত মনস্তাপে ভুগেছেন। তিনি ৫৭ বা ৫৮ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন এবং মদীনার কবরস্থান বাকীতে সমাহিত হন।
হুদায়বিয়ার সন্ধি : মুসলমানদের অগ্নিপরীক্ষা:
উম্মহাতুল মুমেনীনদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমা রা. জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার কারণে তাকে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টার মর্যাদায় স্মরণ করা হয়। নবীজি মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবীর বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন কুরাইশরা তাকে মক্কা প্রবেশ ও উমরা পালন করতে দেবে না। তিনি আলোচনার জন্য মক্কার ধনাঢ্য ব্যক্তি হযরত উসমানকে পাঠান। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কুরাইশদের সাথে শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু বাহ্যত এই চুক্তি ছিল মহানবী ও মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর। শান্তির স্বার্থে ও ভবিষ্যতের বৃহত্তর সুফলের আশা নিয়ে নবীজি এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্ত ও চুক্তি স্বাক্ষরকালে মক্কার মুশরিকদের ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণে মুসলমানরা ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিল। বিপুল সংখ্যক জানবাজ যোদ্ধা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও মহানবীর পক্ষ হতে মুশরিকদের অযৌক্তি সব শর্ত মেনে নেয়াকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না, হযরত উমর রা. এর মত বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহাবীও। শেষ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষর হল। শর্ত অনুযায়ী মুসলমানরা উমরা পালন না করেই ফেরত যাবে। মক্কার হেরেমে কুরবানীর জন্য যেসব পশু তারা সাথে এনেছিল সেগুলো হুদায়বিয়াতেই যবাই করতে হবে। এখানেই উমরার ইহরাম খুলতে হবে।
রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টার মর্যাদায় হযরত উম্মে সালামা রা.
নবীজি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন, তোমরা কুরবানীর পশু জবাই কর। মাথার চুল ছেঁটে ফেল। ইহরাম খুলে স্বাভাবিক হয়ে যাও। কিন্তু আশ্চর্য যে, যারা নিজের জান বাজি রেখে হযরতের নির্দেশে প্রাণ দিতে হুদাইবিয়া প্রান্তর পর্যন্ত এসেছেন, তারা এখন হযরতের আদেশ পালনে তৎপর হচ্ছেন না। নবীজি তার আদেশটি তিনবার ঘোষণা করলেন। কিন্তু কেউ আদেশ পালনে অগ্রসর হয় না। এ অবস্থা দেখে নবীজি চিন্তিত মনে তাঁবুতে ঢুকে উম্মে সালামাকে লোকদের অবস্থার কথা জানালেন। নেতৃত্বের আনুগত্য ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর চেয়ে গভীর ও জটিল সংকট আর কিছু হতে পারে না। এই সংকট সমাধানে প্রচ- আত্মবিশ^াস নিয়ে এগিয়ে এলেন নবীজির যোগ্য সহধর্মীনী আমাদের মা উম্মে সালামা। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান যে তারা আপনার আদেশ পালন করুক। তাহলে আপনি তাদের কারো সাথে একটি কথাও বলবেন না। শুধু সবার সামনে গিয়ে আপনার উটনীটি নহর (জবাই) করুন। তারপর আপনার নাপিতকে ডেকে আপনার মাথা মু-ানোর ব্যবস্থা করুন। এই পরামর্শ পেয়ে নবীজি তাঁবু হতে বের হলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের উটনী নহর করলেন। তারপর নাপিত ডেকে মাথা মু-ন করলেন। লোকেরা যখন এই দৃশ্য দেখল, সবাই তাদের কুরবানীর পশু নহর করল। একজন আরেকজনের মাথা মু-ন শুরু করল। এতক্ষণ তারা ভাবছিল যে, মুশরিকদের সাথে দৃশ্যত অবমাননাকর চুক্তি হয়ত পুনর্বিবেচনা হবে, পশু জবাই ও মাথা মু-নের জন্য নবীজির আদেশ পালনে তাই তারা ইতস্তত করছিল। কিন্তু যখন প্রমাণ হল যে, নবীজি তাঁর সিদ্ধান্ত ও আদেশের ব্যাপারে অবিচল তখন তারা সেই আদেশ পালনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বস্তুত জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে হযরত উম্মে সালমার এই বিচক্ষণতা ও ভূমিকা মুসলিম মহিলাদের জন্য সামাজ ও জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে।
হাবশায় হিজরতে মহিলাদের ভূমিকা:
এ পর্যন্ত আমরা তিনজন উম্মুল মুমিনীনের ভূমিকার উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেছি। এর বাইরে সাধারণ মুসলিম মহিলারাও দ্বীনী দায়িত্ব পালনে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা অনেক বিস্তৃত ও গৌরবজনক। নবুয়াতের ৫ম বর্ষে মক্কায় যখন মুশরিকদের আত্যাচার নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল তখন নবীজির আদেশে দুই দফায় মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেন। দেখা যায় দেশত্যাগের কঠিন কষ্ট যারা মাথায় নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশ জনের মত ছিলেন মহিলা। ইসলামের জন্যে প্রথম যুগের মুসলিম মহিলাদের এই আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে মুসলিম মহিলারা পিছপা হন নি।
মক্কায় মজলুম পাঁচ কৃতদাসী:
আবু বকর সিদ্দিক রা. মক্কায় যারা আল্লাহর পথে আসার কারণে নির্যাতিত হচ্ছিল তাদের মধ্যে সাতজন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলাকে মুক্তি দান করেন। পুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেলাল ইবনে রেবাহ ও আমের ইবনে ফাহির, যাকে গারে সৌরে আত্মগোপন অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহায় আসা যাওয়ার ব্যাপারে নিজের জন্য নিরাপদ মনে করেছিলেন। তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং বী’রে মাউনার হত্যাকা-ের সময় তিনি শাহাদত বরণ করেন। পাঁচজন মহিলার মধ্যে ছিলেন হযরত নাহদিয়া ও তাঁর মেয়ে, উম্মে উমাইস ও বনি আমর ইবনে মুআম্মাল এর দাসী ও যুনাইরা। বর্ণিত আছে, যুনাইরা ছিলেন দুর্বল দৃষ্টিশক্তির একজন মহিলা। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর শায়বা ইবনে রাবিয়া, উতবা ইবনে রাবিআ ও উমাইয়া ইবনে খালাফ প্রমূখ কুরাইশ নেতা দলবলসহ তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। তাকে বসিয়ে নানা কথা বলে হাসাহাসি করত। তারা বলত যে, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ যে ধর্ম নিয়ে এসেছে তা যদি ভাল হত তাহলে যুনাইরা আমাদের পেছনে ফেলে সেদিকে যেতে পারত না। এ মর্মে কুরআনের একটি আয়াত নাযিল হয়। এক সময় যুনাইরার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ চলে গেল। তখন কুরাইশের নেতারা বলতে লাগল, তুমি লাত ও ওজ্জার ধর্মের বিরোধীতা করেছ; এ জন্যে লাত ও ওজ্জা তোমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে। যুনাইরা তাদের জবাবে বলতেন, না, আল্লাহর কসম, তারা আমার কোনো ক্ষতি করে নি এবং আমার কোনো ক্ষতি করার শক্তি ওদের নাই। পরবর্র্তীতে আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
প্রথম মহিলা শহীদ সুমাইয়া রা.:
ইসলামের জন্য পুরুষদের পাশাপশি মহিলাদের আত্মত্যাগের কাহিনী বড়ই করুণ। হযরত সুমাইয়া রা. ছিলেন আবু হুযাইফার বাঁদী। ইয়াসের তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঘর আলোকিত করে আম্মার নামক ছেলে সন্তান। আম্মার রাসূলুল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দাওয়াত পেয়ে তাঁর পিতা ইয়াসের এবং পরে মা সুমাইয়া ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেন। অত্যন্ত করুণ ও কঠিন অবস্থায় এই পরিবার নবীজির প্রতি ঈমান আনয়ন করে। মুশরিকরা এই দুর্বল পরিবারটির উপর তাদের নৃশংসতার মাত্রা পরীক্ষা করে। মুশরিকরা ইয়াসির পরিবারের উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে অন্যদের কাছে এই বার্তা দিতে চেয়েছিল যে, মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করলে এ রকম মাসুল গুণতে হবে। সুমাইয়ার উপর তারা যে নির্যাতন চালায় তা ছিল লোমহর্ষক, অবর্ণনীয়। বলা হয়েছে, সুমাইয়ার দুই পা দুই উটের সাথে বেঁধে উট দুটিকে বিপরীত দিকে ধাবড়ানো হয়। আরো বর্ণিত আছে, মুশরিকরা হযরত সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে বর্শা ঢুকিয়ে তাকে শহীদ করেছিল। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের এই ত্যাগ ও ভূমিকা আজকের বিশে^র মুসলিম মহিলাদের জন্য গৌরবের।
হযরত উমর রা. এর খুতবার প্রতিবাদ করলেন নারী:
নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে ইসলাম দেশে দেশে বিজয় ও বিস্তার লাভ করেছে। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে কখনো মহিলাদেরকে অন্তপুরের অবরোধবাসীনী হয়ে নির্বিকার করে রাখা হয় নি। সমাজ জীবনে তাদের সক্রিয় ভূমিকার একটি উদাহরণ হযরত উমর রা. এর খেলাফতকালের একটি ঘটনা। হযরত উমর রা. মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন। মহিলাদের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বিয়েকে সহজ করার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। বলছিলেন যে, বিয়েকে সহজ করতে হলে বিরাট অঙ্কের মোহরানার প্রবণতা ছাড়তে হবে। জুমার নামাযে উপস্থিত একজন মহিলা দাঁড়িয়ে গেলেন। খলিফার বক্তৃতার প্রতিবাদ করে বললেন, কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা মহিলাদেরকে বিরাট অঙ্কের মোহরানার ব্যবস্থা রেখেছেন। কাজেই আল্লাহ যেখানে আমাদেরকে বিরাট অঙ্কের মোহরানা দেয়ার কথা বলেছেন সেখানে তা কেড়ে নেয়ার আপনি কে? চিন্তা করা যায়, ভরা মসজিদে খলিফার ভাষণের সরাসরি প্রতিবাদ করছেন একজন মহিলা। বিশেষজ্ঞগণ এই ঘটনাকে মুসলিম মহিলাদের পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। সমাজের বৃহত্তর আঙ্গিনায়, জাতীয় জীবনে, সাহিত্য সংস্কৃতিতে, শিক্ষা ও চিকিৎসায় এমনকি যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম মহিলাদের অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।
আধ্যাত্মিক অঙ্গনে নারী:
আমরা এখানে আধ্যাত্মিক অঙ্গনে মহিলাদের অবদানের ব্যাপারে আলোকপাত করতে চাই। ইসলামের ইতিহাসে আধ্যাত্মিক সাধনায় শিরোমণি একজন মহিলার নাম সবাই জানি। তিনি হলেন রাবেয়া আদবিয়া। হিজরী প্রথম শতকে তিনি সওয়াবের আশায় বা আযাবের ভয়ে নয়, আল্লাহর মহব্বতে ইবাদত বন্দেগী করার দর্শন প্রচার করেন।
মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রহ. ইসলামের ইতিহাসের প্রাতঃস্মরণীয় একজন মনিষী। তার রচিত শরহে জামী আরবি ব্যাকরণের অনবদ্য গ্রন্থ। তিনি শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার রহ. এর তাযকিরাতুল আউলিয়ার আদলে একটি আউলিয়া জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন নাম নাফাহাতুল উন্স। এই কিতাবের শেষ ভাগ তিনি বরাদ্দ করেছেন আধ্যাত্মিক জগতের বরেণ্য সাধক রমনীদের বিষয়ে।
বইয়ের ৭১৬ পৃষ্ঠা হতে শুরু হয়েছে পুরুষ সাধকদের মর্যাদায় উন্নীত আধ্যাত্মিক মহিলা সাধকদের জীবন চরিত আলোচনা। সেই আলোচনা শেষ হয়েছে গ্রন্থের শেষভাগে ৫৭৮ পৃষ্ঠায়। মোট ৩৩ জন মহিলা সাধকের জীবন চরিত তিনি আলোচনা করেছেন তন্মধ্যে প্রথমজন রাবেয়া আদবিয়া বা রাবেয়া বসরী রহ. আর যার জীবন চরিত নিয়ে গ্রন্থের যবনিকাপাত করেছেন তিনি হলেন ইমরাআত ফারসিয়া র। মওলানা জামীর এই বর্ণনা প্রমাণ করে আল্লাহর প্রেমের আধ্যাত্মিক সাধনায় মহিলারা কত অগ্রণী ছিলেন এবং মানব সভ্যতার নির্মাণ ও পরিচর্যায় তাদের অবদান কতখানি সুদূর প্রসারী।
মা হাজেরার অনুকরণের উপর ইসলামের ভিত নির্মিত:
শুনে প্রথমে অবাক হবেন যে, ইসলামের যে বিশ্বজনীন ব্যবস্থা তার ভিত নির্মিত হয়েছে একজন মহিলার অবদানের উপর। ইতিহাস বলে, হযরত ইবরাহীম আ. দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত হাজেরা আ. কে কোলের শিশু ইসমাঈলসহ রেখে এসেছিলেন জনমানবহীন মক্কার মরুপ্রান্তরে। ইব্রাহীম আ. বাস করতেন বর্তমান ফিলিস্তিনে। সেখান থেকে গিয়ে তিনি শিশু ইসমাইলকে মায়ের কোলে রেখে আসেন ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে বর্তমানে কাবাঘর ও হেরেম শরীফ প্রতিষ্ঠিত। জনমানবহীন খাদ্য ও পানীয় শুন্য একটি মরুভূমিতে স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে রেখে আসা ইব্রাহীমের জন্য যতখানি অসহনীয় ছিল তার চেয়েও বিস্ময়কর ছিল হযরত হাজেরার এমন নির্বাসিত জীবন মেনে নেয়া। অথচ আল্লাহর আদেশ বলে তারা হাসিমুখে বরণ করে নেন যাবতীয় মানসিক ও দৈহিক কষ্ট। ইবরাহীম আ. এর প্রত্যয় ছিল যেহেতু এই কাজ আল্লাহর হুকুমে আঞ্জাম দিয়েছি বাকিটুকু তিনি দেখবেন।
একটি থলিতে রাখা খেজুর ও মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে কোলের যাদুর প্রাণ নাশের আশংকায় হযরত হাজেরা অস্থির হয়ে যান। পানির সন্ধান পাবেন আশায় একবার সাফা পাহাড়ের উপর উঠেন, আবার মারওয়া পাহাড়ের দিকে দৌঁড়ে যান। মনে হয় পানি সাফা পাহাড়ের উপর টলমল করছে। আবার দৌঁড়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে নিরাশ হন। মনে হচ্ছে পানি মারওয়া পাহাড়ে ঝিলমিল করছে। আসলে মরুভূমির প্রখর রোদে মরিচিকার মায়াজালকে পানির অথৈ তরঙ্গ বলে ভ্রম হচ্ছিল। এভাবে হাজেরা আ. সাত বার দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌঁড়ান।
শেষবারে লক্ষ করেন, শিশুকে যেখানে রেখে পানির জন্য ছুটাছুটি করছেন সেখানে ইসমাঈলের পায়ের নিচ থেকে পানির ঝর্ণা উৎসারিত হচ্ছে। হাজেরা তাড়াতাড়ি সেই ঝর্ণার চারপাশে আল তুলে দেন। এই ঝর্ণাই বর্তমান যমযম কূপ। সেই কূপকে কেন্দ্র করে মক্কায় জুরহুম সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠে। কাবাঘর নির্মিত হয়। হজের প্রবর্তন হয়। তখন থেকে যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন, যত আলেম ওলী এসেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন, প্রতি বছর লাখ লাখ হাজি হজ করেন, সারা বছর ওমরা করেন, তাদের সবাইকে মহিয়সী নারী বিবি হাজেরার অনুকরণ করতে হয়। তিনি যেভাবে দৌঁড়িয়েছেন সেভাবে সাফা মারওয়ায় সায়ী করতে হয়। তারপর মা হাজেরার স্মৃতিধন্য যমযমের পানি পান করে আমরা প্রাণ জুড়াই। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নারীদের ভূমিকার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে? আর নারীর প্রতি ইসলাম যে সম্মান দিয়েছে তা কি মানুষের কল্পনায় আসতে পারে?
লেখক: ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী
সাবেক শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কলামিস্ট, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।